স্টিফেন হকিংও স্কুলে পড়তেন। স্কুলের নাম সেইন্ট অ্যালবান্স স্কুল। স্কুলটি সম্প্রতি তহবিল সংগ্রহে নেমেছে। আর সেই আয়োজনে বক্তৃতা দেবেন স্বয়ং স্টিফেন হকিং। এমন কাজ কিন্তু একেবারে তার চরিত্রের বিপরীত। আর এই ঘটনাই প্রমাণ করে, স্কুলটির প্রতি তার আবেগ এখনও কত গভীর! এখন প্রশ্ন হল, স্কুলে থাকতে স্টিফেন হকিং কেমন ছিলেন? কেমনইবা ছিল তার ছোটবেলার ভালোবাসার স্কুল? এসব নিয়েই ‘দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট’ এ লিখেছেন তার সহপাঠী মাইকেল চার্চ। সেই লেখাটিই বাংলায় তর্জমা করে দেওয়া হল।
স্টিফেন হকিংয়ের সঙ্গে সেইন্ট অ্যালবান্স স্কুলে আমরা যারা পড়তাম, সেসব দিনের স্মৃতি আমাদের আজও আনন্দ জোগায়। যেমন আনন্দ জোগায় স্টিফেনকেও। ছোটখাটো গড়নের স্কুল পড়ুয়া স্টিফেনের মধ্যে বেশ আনাড়িপনা ছিল। তবে সে বেশ দক্ষ ছিল সাইকেল চালানোয়। বিশেষ করে ধীরে সাইকেল চালানোতে সে ছিল রীতিমতো দক্ষ। পড়াশোনাতেও ছিল বেশ চটপটে। বিজ্ঞানের প্রতি তার পরিষ্কার ঝোঁক ছিল। তবে সে যে বিজ্ঞানী হিসেবে এমন অসম্ভব উচ্চতায় উঠবে, তার কোনো ইঙ্গিত কিন্তু সে সময় ছিল না।
হকিং খুব দ্রুত কথা বলত। কখনও কখনও তার স্বউদ্ভাবিত ভাষায়। যেমনঃ তার একটি শব্দ ছিল, উচ্চারণ অনেকটা এ রকম, ‘স্লিটাউট’।
মনোপলি খেলার নিয়ম কানুন তার বড় একঘেয়ে লাগত। সে বরং এটার মতো আরও অনেক বোর্ড গেইম বানিয়েছিল। সে ছিল, যাকে বলা যায়, নতুন নতুন বোর্ড গেইম উদ্ভাবনে সিদ্ধহস্ত। তার উদ্ভাবিত একটি বোর্ড গেইমের বিষয় ছিল মধ্যযুগীয় যুদ্ধ। আর সে খেলায় যুদ্ধ করার সময় যুদ্ধের আইন কানুন, বিভিন্ন বিধি নিষেধ, বাজেট, বাহিনি ব্যবস্থাপনা সবই বিবেচনায় রাখতে হত। সব মিলিয়ে খেলাটা এমনই জটিল ছিল, মাঝে মাঝে একেবার ছক্কা ছোড়ার পর কী করতে হবে, তা ঠিক করতেই পেরিয়ে যেত আধ ঘণ্টার মতো।
কমিউনিস্ট লিগের সদস্যও ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই সে আমাদের নিয়ে যোগ দিয়েছিল আলডারম্যাস্টন মার্চে। পরমাণু শক্তি বিরোধী এই কর্মসূচির কারণেই সম্ভবত সে দীর্ঘদিন দলটির প্রতি অনুগত ছিল।
আমাদের সঙ্গে দুজন তরুণ বিজ্ঞানী পড়ত। ওরা তার ভবিষ্যত সম্ভাবনা সম্পর্কে আঁচ করতে পেরেছিল। আমি অবশ্য তেমন বিজ্ঞান মনস্ক নই। কিন্তু বিজ্ঞানে তার এই সম্ভাবনার দিকটি আমি টের পাই এক বিকেলে। আমি সেদিন গভীর চিন্তায় মগ্ন। জীবনের মানে খুঁজতে ছিলাম। হঠাৎ করেই আবিষ্কার করলাম, ১৬ বছরের স্টিফেন এক অসাধারণ উচ্চতা থেকে আমার সঙ্গে তর্ক করছে। সব মিলিয়ে তার অক্সফোর্ড জীবনে সে বেশ কুখ্যাতই হয়ে উঠেছিল। বিশেষত তার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের কারণে।
তার জীবনের কাহিনি বলতে গেলে বারবার যে প্রসঙ্গটা বাদ পড়ে, সেটা হচ্ছে তার স্কুল "সেইন্ট অ্যালবান্স স্কুল"। অবশ্য স্টিফেন নিজে বারবার ডিক তাহতার উল্লেখ করেছে। জাতিতে আর্মেনিয়ান এই ডিক তাহতা ছিলেন আমাদের গণিতের শিক্ষক। কৈশোরেই স্টিফেন তার সঙ্গে মিলে বিশাল একটি প্রোটোপ্ল্যানেট কম্পিউটার বানিয়েছিল। এই ঘটনা পরবর্র্তীতে তার জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। সকলের জীবনেই তার স্কুল একটি বিশাল অনুপ্রেরণা, তার প্রভাবও অপরিসীম। কিন্তু স্টিফেনের জন্য এই স্কুল আরেকটু বেশি কিছুই ছিল। এখানেই স্টিফেন শেষবারের মতো স্বাভাবিক জীবনযাপন করেছিল। এখানেই তার সেই সোনালি দিন গুলো কেটেছিল, যখন সে দৌড়াত, লাফাত ঝাঁপাত, বলরুমে নাচত, টেনিস খেলত।
স্কুলের বন্ধুদের স্মৃতি তার সারা জীবনের সঙ্গী। এখনও ক্যামব্রিজে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে সেসব দিনের গল্প করে সে। একে একে বলে প্রায় সব সহপাঠীর কথাই। বিভিন্ন ঘটনার দিন তারিখ ঠিক ঠিক মনে পড়ে না বলে বিরক্তও হয়। স্কুলের প্রতি তার ভালোবাসা যে কত গাঢ়, সম্প্রতি তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিশেষ একটি ঘটনায়। স্কুলের বিজ্ঞান জাদুঘরের জন্য ফান্ড তোলা হচ্ছে। আর সে উপলক্ষে সে একটি বক্তৃতা দেবে, যা তার চরিত্রের সঙ্গে একদমই যায় না।
পঞ্চাশের দশকেও এই সেইন্ট অ্যালবান্স স্কুল সরকারি অনুদান পেত। কিছু আবাসিক ছাত্রও তাতে ছিল। আর স্কুলটি কেবল পড়াশোনার কাজেই ব্যবহৃত হত না। স্কুলের সবচেয়ে বড় ক্লাস রুমটি রাতে ব্যবহৃত হত গির্জা হিসেবে। তবে স্কুলের আসল মন্দির ছিল লাইব্রেরিটা। ওখানে অন্যান্য বইয়ের মধ্যে এমনকি জনসন’স ডিকশনারির প্রথম এডিশনও ছিল।
যুদ্ধোত্তর ব্রিটিশ সরকারের আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে স্কুলটির পদ্ধতিতে বেশ কিছু পরিবর্তন আসে। বেশি জোর দেওয়া হয় বিজ্ঞানের উপর। পরীক্ষার মাধ্যমে অর্ধেক শিক্ষার্থী বিনা খরচে পড়ার সুযোগ পায়। বাকিদের পড়তে হয় টাকা দিয়ে। টাকা দিয়ে পড়লেও, পরীক্ষা দিয়েই ভর্তি হতে হত। তার উপর হার্টফোর্ডশায়ারে তখন মধ্য ইউরোপ থেকে প্রচুর মানুষ এসেছে বাস করতে, যাদের অনেকেই রীতিমতো শিক্ষিত। সব মিলিয়ে, স্কুলটিতে তখন প্রতিভাবানদের ছড়াছড়ি। আর স্টিফেন তার শেষ জীবনীতে তো বলেছেই, সে কখনই স্কুলটির সেরা ছাত্রদের কাতারে ছিল না। তার ভাষায়, প্রথম কাতারের ছাত্রদের দৌড়ে সে কখনও অর্ধেক রাস্তাও পেরুতে পারেনি। স্কুলের ‘তারকা’ বলতে যেটা বোঝায়, সেইন্ট অ্যালবান্সে সে কখনওই তা ছিল না।
অক্সফোর্ড আর ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশিপকে লক্ষ্য ধরে স্কুলটির পড়াশোনায় বেশ কড়াকড়ি আনা হয়েছিল। একাদশ শ্রেণিতে যারা পড়ত, তাদের সবাই নিঃসন্দেহেই প্রতিভাবান ছিল। তবু যারা পিছিয়ে পড়ত, ধরেই নেওয়া হত, তারা ব্যর্থ। স্কুলটিতে খেলাধুলাও বাদ পড়ত না। সপ্তাহে দুদিন বিকেলে বাধ্যতামূলক খেলার ব্যবস্থা ছিল। সেই খেলাধুলার মধ্যে এমনকি ১২ ডিগ্রি শীতের মধ্যে সাঁতারও ছিল। অবশ্য স্টিফেন সেসব খেলাধুলায় তেমন ভালো ছিল না। স্কুলে জোর দেওয়া হত আঁকাআঁকির প্রতিও। সব মিলিয়ে অবস্থা এমন ছিল যে, তখন সেইন্ট অ্যালবান্সে মাস্টার্স করার জন্য শিক্ষার্থীদের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চেয়েও বেশি প্রতিভাবান হতে হত।
তবে স্কুলটির ছাত্রদের অনেকেই ছিল যাকে বলে ছিটগ্রস্ত। তার কারণও ছিল। অনেকের পরিবারই সাক্ষী ছিল কোনো না কোনো বিশ্বযুদ্ধের। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডানকির্ক যুদ্ধের সাক্ষী ছিল অনেকের পরিবার। তাদের অনেকের চরিত্র এত বেশি অদ্ভুতুড়ে ছিল, এখনকার সময়ে সেসব মেনে নেওয়াও কঠিন হত। আর স্কুলের বিচার আচারের ব্যাপার গুলোও ছিল যাকে বলে নির্মম। শিক্ষকদের হাতে মার খাওয়া ছিল খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। শিক্ষকরা ছাত্রদের বেত মারত অহরহ। একটা ঘটনা আমার মনে পড়ে। এক শিক্ষক একবার দৌড়ে গিয়ে এক ছাত্রকে লাথিই মেরে বসে। ছাত্রটি হকচকিয়ে ঘুরে দাঁড়ালে শিক্ষক বলে ওঠেন, “আহা! আমার পা টা কীভাবে যেন ভুল পথে চলে গেল!”
শাস্তির এই চড়া সুরটি বেঁধে দিয়েছিল স্কুল প্রধান ডব্লিউ টি মার্শ স্বয়ং। অ্যাথলেট মার্শ নৌযুদ্ধে অংশ নিয়ে বেশ নাম করেছিল। প্রতিদিনের সকালের সমাবেশ সে শেষ করতেন নিষ্ঠুর কোনো কাহিনি বলে। যাতে তার প্রতি শিক্ষার্থীদের আনুগত্য আরও বাড়ে। এমনি একটি গল্প ছিল সাইকেল দুর্ঘটনায় এক বুড়ো আলবেনিয়ানের মৃত্যু নিয়ে। গল্পটি সে এতবার বলেছিল, সেটি আমাদের কাছে গ্রিক নাটকের মতো ক্ল্যাসিক একটি কাহিনি হয়ে গিয়েছিল। গল্পের শেষে সে এই বলে গর্জে উঠত, “অনেকে বলবে ঘটনাটি খুব করুণ। তা মোটেই ঠিক নয়। বুড়োর পরিবারের জন্য ঘটনাটি দুর্ভাগ্যের, দুঃখের। কিন্তু এটি ট্র্যাজিক ঘটনা নয়।” আর তারপর সে অ্যারিস্টটলের ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা বোঝাতে শুরু করতেন। বোঝাতে শুরু করতেন, কীভাবে সেই বুড়োর নিজের ভুল তার দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাবেশে মাঝে মাঝে ধর্মোপদেশও দেওয়া হত। বিশেষ করে যখন লেট লতিফরা থাকত।
পঞ্চাশের দশকেই আমরা আঠারতে পা দিলাম। মনে জোয়ার এল দেশের জন্য কাজ করার। সেইন্ট অ্যালবান্স তখন প্রতি শুক্রবার আক্ষরিক অর্থেই মিলিটারি একাডেমিতে রূপান্তরিত হত। আমরা সেই একাডেমির মিলিটারি। সবাই মিলিটারিদের মতো পোশাক পরে প্রশিক্ষণ নিতাম। সেই পোশাকে স্টিফেনকে রীতিমতো অদ্ভুত দেখাত। যেন কোনো কৌতুক অভিনেতা। অল্প কয়েকজন সেই প্রশিক্ষণ এড়াতে পারত। অনেকেই তাদের বাবা মার অনুরোধে। যারা সেই প্রশিক্ষণে অংশ নিত না, তাদের নিয়ে সবাই ঠাট্টা তামাশা করত। এর বদলে তাদের বিকেলটা যে কাজে পার করতে হত, সেটাও কোনো আরামদায়ক কাজ ছিল না।
আমরা যারা প্রশিক্ষণ নিতাম, তাদের যেটা করতে হত, রানিং কিট পরে স্কয়ার ব্যাশ আর রুট মার্চ করতে হত। আর বছর শেষে ক্যাটেরিকে আমাদের একটি আর্মি ক্যাম্প হত। সেখানে আমাদের মেশিনগানে গুলি ছুড়তে হত। কিন্তু এয়ারপ্লাগ দেওয়া হত না। বলা হত, মেশিনগানে গুলি ছোড়ার সময় মেয়েলিরাই এয়ারপ্লাগ ব্যবহার করে। ফলাফল হিসেবে অনেকেরই কানে চিরস্থায়ী সমস্যা হয়ে গিয়েছিল। আমিও তাদের একজন। স্টিফেন অবশ্য প্রথমবার নিজে নিজেই ব্লটিং পেপার দিয়ে একটা এয়ারপ্লাগ বানিয়ে নিয়ে এসেছিল। গুলি ছোড়ার সময় তাপে এয়ারপ্লাগটি পুড়ে যায়। পরে স্টিফেনকে ক্যাম্প ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়।
এসব গল্প শুনে মনে হতে পারে, সেইন্ট অ্যালবান্স মর্ত্যরে বুকে এক টুকরো নরক ছিল। আমরা হয়তো আমাদের স্কুলকে ভীষণ ঘেন্না করতাম। কোন ভাবেই নয়। সেইন্ট অ্যালবান্স হয়ত এক বদ্ধ জায়গা ছিল, সেখানে হয়ত স্বাধীনতার অভাব ছিল, নিয়মের কড়াকড়ি অনেক বেশি ছিল, কিন্তু একই সঙ্গে আমাদের স্কুল প্রাঙ্গণ ছিল গানে নাটকে আনন্দে ভরপুর। স্কুল থেকে তরুণ ঋদ্ধ শিক্ষকরা নিয়মিতই চলে যেতেন। তারা চলে যেতেন মূলত স্কুল প্রধান মার্শের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায়। তবু এটা নিশ্চিত করা হত যে, আমাদের শিক্ষায় যেন কোনো ব্যাঘাত না ঘটে। নিশ্চিত করা হত যে, আমরা বুদ্ধি বৃত্তিক চর্চার মধ্যেই আছি।
বিজ্ঞানের জগতে আমূল পরিবর্তন আনা বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংয়ের জীবনে এই স্কুলের যে বিশাল অবদান আছে, তা অবিসংবাদিত। তার দর্শনেও প্রভাব আছে প্রেশার কুকারের সঙ্গে তুলনীয় এই স্কুলটার, "সেইন্ট অ্যালবান্স স্কুলের"।
লেখকঃ নাবীল অনুসূর্য।
সম্পাদনায়ঃ জানা অজানার পথিক।

.jpg)




.jpg)





.jpg)
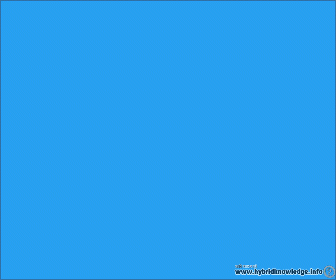



কোন মন্তব্য নেই:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন