শীতল পাটিঃ
"আসুক, আসুক বেটির দামান কিছুর চিন্তা নাইরে
আমার দরজায় বিছায়া থুইছি কামরাঙ্গা পাটি নারে।"
আমার দরজায় বিছায়া থুইছি কামরাঙ্গা পাটি নারে।"
কবি জসীমউদ্দিনের নক্শি কাঁথার মাঠ কবিতায় উল্লেখিত কামরাঙ্গা পাটিই এ দেশের ঐতিহ্যবাহী শীতল পাটি। প্রাচীনকালে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা ছিল না। তাই গরমের দিনে কাঁথা বা তোষকের উপর শোয়ার জন্য এক ধরনের পাটি ব্যবহৃত হত। চিকন চিকন বেতিতে বোনা সে পাটিতে পিঠ এলিয়ে দিলেই শরীর মন শীতল হয়ে যেত। এজন্য সে পাটির নাম কালক্রমে হয়ে যায় শীতল পাটি। মুর্তা বা পাটিপাতা গাছের বেতি তুলে সে পাটি নকশা করে বোনা হয় বলে ওর আর এক নাম নকশি পাটি।
এ দেশের জলাভূমি বা নিচু স্যাঁতসেতে জমিতে ছোট ছোট কঞ্চির মত এক ধরনের গাছ জন্মে। পাতা দেখতে অনেকটা কাঁঠাল পাতার মত। এ গাছের নামই বেতিগাছ। নোয়াখালীতে বলে মেস্তাগ, কুমিল্লায় মোতাবাইক, সিলেটে মোতা/মুর্তা, মুন্সিগঞ্জে মোত্রাবেত, ঝালকাঠিতে পাইত্তা। অন্য নাম মুর্তাবেত, মোতাবেত, পাটিবেত ইত্যাদি। জুন-জুলাইতে গাছে ফুল আসে, সেপ্টেম্বরে গাছ পাকে বা কান্ড শক্ত হয়। তখন কেটে পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়। পরে তা থেকে বেতি তোলা হয় ও সেই বেতি দিয়ে পাটি বোনা হয়। শোয়ার পাটি ছাড়াও জায়নামাজ, দেয়ালমাদুর, বসার আসন ইত্যাদিও তৈরি করা হয়। ফুল,মসজিদ, লতাপাতা, প্রাণি ও পাখিদের ছবি দিয়েও অলংকৃত করা হয়। তবে মানানসই রঙে বিভিন্ন আল্পনা দিয়ে যেসব শীতলপাটি বোনা হয় সেগুলো দেখতে খুবই সুন্দর। সেগুলোকে বলে নকশি পাটি।
চিত্রানুযায়ী বিভিন্ন পাটির বিভিন্ন নামও দেয়া হয়। যেমন খেলাঘর, আসমান তারা, জমিনতারা, তাজমহল ইত্যাদি। আছে মোটা পাটি ও চিকন পাটি। শীতল পাটি যারা বোনেন তাদের বলে পাটিয়াল। হিন্দু মসলমান যে কেউ পাটিয়াল হতে পারে। সাধারণতঃ উত্তরাধিকারসূত্রেই পাটিয়াল হয়। অধিকাংশ শীতল পাটির আকার হয় ৬র্ ত্ম৯র্ । দাম দুশ টাকা থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত হয়। সিলেট, ময়মনসিংহ, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, ফেনী, টাঙ্গাইলে বেশি শীতল পাটি বানানো হয়। ফরিদপুরে শীতল পাটিকে বলে সাতৈর পাটি। শীতল পাটি বাংলাদেশের একান্তই নিজস্ব ঐতিহ্য। বিদেশে শীতল পাটি তৈরি হয় এমন কথা শোনা যায়নি।
চিত্রানুযায়ী বিভিন্ন পাটির বিভিন্ন নামও দেয়া হয়। যেমন খেলাঘর, আসমান তারা, জমিনতারা, তাজমহল ইত্যাদি। আছে মোটা পাটি ও চিকন পাটি। শীতল পাটি যারা বোনেন তাদের বলে পাটিয়াল। হিন্দু মসলমান যে কেউ পাটিয়াল হতে পারে। সাধারণতঃ উত্তরাধিকারসূত্রেই পাটিয়াল হয়। অধিকাংশ শীতল পাটির আকার হয় ৬র্ ত্ম৯র্ । দাম দুশ টাকা থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত হয়। সিলেট, ময়মনসিংহ, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, ফেনী, টাঙ্গাইলে বেশি শীতল পাটি বানানো হয়। ফরিদপুরে শীতল পাটিকে বলে সাতৈর পাটি। শীতল পাটি বাংলাদেশের একান্তই নিজস্ব ঐতিহ্য। বিদেশে শীতল পাটি তৈরি হয় এমন কথা শোনা যায়নি।
শোলাঃ
বাঙালির ঐতিহ্য ও লোকশিল্পের একটি অংশ শোলা। এ শোলা আমাদের দেশজ গুল্ম জাতীয় এক প্রকার উদ্ভিদও বটে। শোলা নরম ও হালকা বলে ইংরেজিতে 'স্পঞ্জ' নামে বেশ পরিচিত। বার মাসে তের পার্বণের দেশ এ বাংলাদেশ। আমাদের দেশে বর্ষাকালে জলাশয় ও নিচু জায়গায় শোলার বংশবিস্তার ঘটে। শোলার চাষ করা হয় না, তা এমনিতেই হয়। অঞ্চলভেদে কোথাও কোথাও এই শোলাকে মালি শোলা এবং ভাট শোলাও বলে থাকে।
শোলার জন্ম নিয়ে আছে লোকবিশ্বাস। দেবতা শিব হিমালয়কন্যা পার্বতীকে বিয়ে করবেন। তিনি বিয়েতে শ্বেতমুকুট পরতে ইচ্ছা পোষণ করলেন। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা তখন মুকুট তৈরির উপাদানের কথা ভাবতেই শিবের ইচ্ছায় এক ধরনের উদ্ভিদের জন্ম নিলো। সেটাই হলো শোলা (ভ্যাতে শোলা) গাছ। কিন্তু বিপত্তি হলো, বিশ্বকর্মা শোলার মতো নরম ও হালকা কিছু দিয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত নন। তখন আবার শিবের ইচ্ছায় জলাশয়ে এক সুকুমার যুবকের আবির্ভাব ঘটল। তাকে আখ্যায়িত করা হলো মালাকার হিসেবে। সেই মালাকার সম্প্রদায়ই শোলাশিল্পী হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শোলার শিল্পকর্ম তৈরি হয়। ঢাকা, মানিকগঞ্জ, কুষ্টিয়া, মাগুরা, নওগাঁ, কুড়িগ্রাম ও বরিশালের দক্ষিণাঞ্চলে একসময় শোলার কাজের জন্য বিখ্যাত ছিল।
টোপর বিয়ের একটি অন্যতম অনুষঙ্গ। এই টোপর সাধারণত শোলা দিয়ে তৈরি হয়।
পরিবেশ-প্রতিবেশ বদলে যাওয়ায় শোলাশিল্পীদের চলছে এখন বড়ই দুর্দিন। শোলাশিল্পের সামগ্রীর ব্যবহার মূলত সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দেখা যায়। তাদের বারো মাসে তেরো পার্বণে, বিয়ের সময়, মুখে ভাতের মুকুট, মালা, দেব-দেবীর অলংকার, কপালি, কদম ফুল, মনসা পূজার পটসহ শোলার তৈরি বিচিত্র সব জিনিস অপরিহার্য। কিন্তু দিনবদলের পালায় বিল-জলাশয়গুলোতে আর শোলা মিলছে না আগের মতো। এ কারণে এই পেশার মানুষেরা বেকার হতে বসেছেন। অন্যদিকে অন্য পেশাতেও খাপখাওয়াতে পারছেন না তাঁরা। অর্ধাহারে-অনাহারে মানবেতর দিনাতিপাত করছেন শোলাশিল্পীরা। আর আমরা হারাতে বসেছি আমাদের এক শিল্পকে। সবার উচিত এই বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা।
বাঙালির ঐতিহ্য ও লোকশিল্পের একটি অংশ শোলা। এ শোলা আমাদের দেশজ গুল্ম জাতীয় এক প্রকার উদ্ভিদও বটে। শোলা নরম ও হালকা বলে ইংরেজিতে 'স্পঞ্জ' নামে বেশ পরিচিত। বার মাসে তের পার্বণের দেশ এ বাংলাদেশ। আমাদের দেশে বর্ষাকালে জলাশয় ও নিচু জায়গায় শোলার বংশবিস্তার ঘটে। শোলার চাষ করা হয় না, তা এমনিতেই হয়। অঞ্চলভেদে কোথাও কোথাও এই শোলাকে মালি শোলা এবং ভাট শোলাও বলে থাকে।
শোলার জন্ম নিয়ে আছে লোকবিশ্বাস। দেবতা শিব হিমালয়কন্যা পার্বতীকে বিয়ে করবেন। তিনি বিয়েতে শ্বেতমুকুট পরতে ইচ্ছা পোষণ করলেন। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা তখন মুকুট তৈরির উপাদানের কথা ভাবতেই শিবের ইচ্ছায় এক ধরনের উদ্ভিদের জন্ম নিলো। সেটাই হলো শোলা (ভ্যাতে শোলা) গাছ। কিন্তু বিপত্তি হলো, বিশ্বকর্মা শোলার মতো নরম ও হালকা কিছু দিয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত নন। তখন আবার শিবের ইচ্ছায় জলাশয়ে এক সুকুমার যুবকের আবির্ভাব ঘটল। তাকে আখ্যায়িত করা হলো মালাকার হিসেবে। সেই মালাকার সম্প্রদায়ই শোলাশিল্পী হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শোলার শিল্পকর্ম তৈরি হয়। ঢাকা, মানিকগঞ্জ, কুষ্টিয়া, মাগুরা, নওগাঁ, কুড়িগ্রাম ও বরিশালের দক্ষিণাঞ্চলে একসময় শোলার কাজের জন্য বিখ্যাত ছিল।
টোপর বিয়ের একটি অন্যতম অনুষঙ্গ। এই টোপর সাধারণত শোলা দিয়ে তৈরি হয়।
পরিবেশ-প্রতিবেশ বদলে যাওয়ায় শোলাশিল্পীদের চলছে এখন বড়ই দুর্দিন। শোলাশিল্পের সামগ্রীর ব্যবহার মূলত সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দেখা যায়। তাদের বারো মাসে তেরো পার্বণে, বিয়ের সময়, মুখে ভাতের মুকুট, মালা, দেব-দেবীর অলংকার, কপালি, কদম ফুল, মনসা পূজার পটসহ শোলার তৈরি বিচিত্র সব জিনিস অপরিহার্য। কিন্তু দিনবদলের পালায় বিল-জলাশয়গুলোতে আর শোলা মিলছে না আগের মতো। এ কারণে এই পেশার মানুষেরা বেকার হতে বসেছেন। অন্যদিকে অন্য পেশাতেও খাপখাওয়াতে পারছেন না তাঁরা। অর্ধাহারে-অনাহারে মানবেতর দিনাতিপাত করছেন শোলাশিল্পীরা। আর আমরা হারাতে বসেছি আমাদের এক শিল্পকে। সবার উচিত এই বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা।
শখের হাঁড়িঃ
একসময় প্রতি গৃহস্ত বাড়িতে শোভা পেত শখের হাঁড়ি। অতিথিরা শখের হাঁড়িতে করে মিষ্টি নিয়ে আসত। নতুন জামাইরা এই হাঁড়িতে করে মিষ্টি-মন্ডা নিয়ে আসত। মাটির হাঁড়িতে বিভিন্ন রকম আলপনা করে এই হাঁড়ি তৈরি করা হয়। গৃহবধুরা শখের বিভিন্ন জিনিস এই হাঁড়িতে রেখে দিত বলে এর নাম শখের হাঁড়ি। এই হাঁড়ি আমাদের ঐতিহ্য। এই হাঁড়ি ছাড়া কোন বাড়ি কল্পনা করা যেত না। উল্লেখ্য, শখের হাঁড়ি শুধু এই বাংলার। পৃথিবীর অন্যত্র শখের হাঁড়ির প্রচলন নেই। তবে দুঃখের বিষয় আমরা এই শিল্প টাকে মেরে ফেলছি।
ধারণা করা হয় আজ থেকে নয় হাজার বছর আগে তৈরি করা মাটির পাত্রের সন্ধান পাওয়া যায় তুরস্কের আনাতলিয়া উপত্যকা খনন করে। ধারণা করা হয় সেটিই পৃথিবীর প্রাচীনতম মাটির পাত্র। তবে আমাদের মাটির পাত্র তৈরির ইতিহাস ততটা প্রাচীন নয়। আনুমানিক সপ্তম থেকে অষ্টম শতকে পাল শাসনামলে উত্তরবঙ্গে মৃৎশিল্পের উৎকর্ষ ঘটে।
শখের হাঁড়ির জন্য রাজশাহী বিখ্যাত। রাজশাহীর বসনপুর গ্রামের সুসান্ত পাল শখের হাঁড়ির চিত্রকর্মের জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন। সুশান্ত পাল যে শখের হাঁড়ি তৈরি করেছেন তা দিয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল।
একসময় প্রতি গৃহস্ত বাড়িতে শোভা পেত শখের হাঁড়ি। অতিথিরা শখের হাঁড়িতে করে মিষ্টি নিয়ে আসত। নতুন জামাইরা এই হাঁড়িতে করে মিষ্টি-মন্ডা নিয়ে আসত। মাটির হাঁড়িতে বিভিন্ন রকম আলপনা করে এই হাঁড়ি তৈরি করা হয়। গৃহবধুরা শখের বিভিন্ন জিনিস এই হাঁড়িতে রেখে দিত বলে এর নাম শখের হাঁড়ি। এই হাঁড়ি আমাদের ঐতিহ্য। এই হাঁড়ি ছাড়া কোন বাড়ি কল্পনা করা যেত না। উল্লেখ্য, শখের হাঁড়ি শুধু এই বাংলার। পৃথিবীর অন্যত্র শখের হাঁড়ির প্রচলন নেই। তবে দুঃখের বিষয় আমরা এই শিল্প টাকে মেরে ফেলছি।
ধারণা করা হয় আজ থেকে নয় হাজার বছর আগে তৈরি করা মাটির পাত্রের সন্ধান পাওয়া যায় তুরস্কের আনাতলিয়া উপত্যকা খনন করে। ধারণা করা হয় সেটিই পৃথিবীর প্রাচীনতম মাটির পাত্র। তবে আমাদের মাটির পাত্র তৈরির ইতিহাস ততটা প্রাচীন নয়। আনুমানিক সপ্তম থেকে অষ্টম শতকে পাল শাসনামলে উত্তরবঙ্গে মৃৎশিল্পের উৎকর্ষ ঘটে।
শখের হাঁড়ির জন্য রাজশাহী বিখ্যাত। রাজশাহীর বসনপুর গ্রামের সুসান্ত পাল শখের হাঁড়ির চিত্রকর্মের জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন। সুশান্ত পাল যে শখের হাঁড়ি তৈরি করেছেন তা দিয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল।
লক্ষ্মীর সরাঃ
একসময় প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়ির দরজায় শোভা পেত লক্ষ্মীর সরা। নতুন ব্যবসায়ীরাও ব্যবসায়ের মঙ্গল কামনায় লক্ষ্মীর সরা ঝুলাতেন। লক্ষ্মীর সরা আমাদের সুপ্রাচীন চিত্রকলার পরিচয় বহন করে। প্রাচীন কালে এখনকার মত ফটো ছিলনা। পোড়ামাটির সরার উপর বিভিন্ন প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহার করে সে কালের শিল্পীরা লক্ষ্মী সরার পটচিত্র আঁকতেন। বাংলার কোন কোন ঘরে বিশেষ করে হিন্দু অব্রাহ্মণ শ্রেণীর লোকেরা শারদ পূর্ণিমা তিথিতে রাতে লক্ষ্মীর পট বসিয়ে পূজা করতেন।
একসময় হিন্দু মুসলমান সব ধর্মের লোকেরা লক্ষ্মীর সরা ব্যবহার করতেন। মুসলমানদের লক্ষ্মীর সরাতে কাবার ছবি সহ বিভিন্ন সংখ্যা মান লেখা থাকত যা গনকী সরা নামে পরিচিত। এই শিল্প বর্তমানে বিলুপ্ত প্রায়। স্বতস্ফুর্তভাবে এখন আর পটশিল্পীরা এ সরা বানাতে চান না। তবুও এটা এখনো দেশের কোন কোন এলাকায় তৈরি হচ্ছে। এ দেশে মোটামুটিভাবে চার রকমের লক্ষ্মীর সরা পাওয়া যায়- ঢাকাই সরা, ফরিদপুরী সরা, সুরেশ্বরী সরা ও গণকী সরা।
ফরিদপুর শহরের লক্ষ্মীপুর এলাকার পালপাড়ার বাসিন্দা মনোরঞ্জন পালের বয়স এখন ৮৫। ১২ বছর বয়সে ঠাকুরদা রজনীকান্ত পালের কাছে তাঁর হাতেখড়ি। আজো তিনি লক্ষ্মীর সরা এঁকে যাচ্ছেন। পল্লীকবি জসীম উদদীন তার কাছে এসেছিলেন। তাকে তিনি লক্ষ্মীর সরা এঁকে উপহার দিয়েছিলেন।
লক্ষ্মী সরার উৎপত্তি এ দেশেই। পণ্য হিসেবে কুমোররা এটি তৈরি করে বিক্রি করলেও লক্ষ্মীর সরা আসলে আমাদের এক জীবন্ত লোক পণ্য।
একসময় প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়ির দরজায় শোভা পেত লক্ষ্মীর সরা। নতুন ব্যবসায়ীরাও ব্যবসায়ের মঙ্গল কামনায় লক্ষ্মীর সরা ঝুলাতেন। লক্ষ্মীর সরা আমাদের সুপ্রাচীন চিত্রকলার পরিচয় বহন করে। প্রাচীন কালে এখনকার মত ফটো ছিলনা। পোড়ামাটির সরার উপর বিভিন্ন প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহার করে সে কালের শিল্পীরা লক্ষ্মী সরার পটচিত্র আঁকতেন। বাংলার কোন কোন ঘরে বিশেষ করে হিন্দু অব্রাহ্মণ শ্রেণীর লোকেরা শারদ পূর্ণিমা তিথিতে রাতে লক্ষ্মীর পট বসিয়ে পূজা করতেন।
একসময় হিন্দু মুসলমান সব ধর্মের লোকেরা লক্ষ্মীর সরা ব্যবহার করতেন। মুসলমানদের লক্ষ্মীর সরাতে কাবার ছবি সহ বিভিন্ন সংখ্যা মান লেখা থাকত যা গনকী সরা নামে পরিচিত। এই শিল্প বর্তমানে বিলুপ্ত প্রায়। স্বতস্ফুর্তভাবে এখন আর পটশিল্পীরা এ সরা বানাতে চান না। তবুও এটা এখনো দেশের কোন কোন এলাকায় তৈরি হচ্ছে। এ দেশে মোটামুটিভাবে চার রকমের লক্ষ্মীর সরা পাওয়া যায়- ঢাকাই সরা, ফরিদপুরী সরা, সুরেশ্বরী সরা ও গণকী সরা।
ফরিদপুর শহরের লক্ষ্মীপুর এলাকার পালপাড়ার বাসিন্দা মনোরঞ্জন পালের বয়স এখন ৮৫। ১২ বছর বয়সে ঠাকুরদা রজনীকান্ত পালের কাছে তাঁর হাতেখড়ি। আজো তিনি লক্ষ্মীর সরা এঁকে যাচ্ছেন। পল্লীকবি জসীম উদদীন তার কাছে এসেছিলেন। তাকে তিনি লক্ষ্মীর সরা এঁকে উপহার দিয়েছিলেন।
লক্ষ্মী সরার উৎপত্তি এ দেশেই। পণ্য হিসেবে কুমোররা এটি তৈরি করে বিক্রি করলেও লক্ষ্মীর সরা আসলে আমাদের এক জীবন্ত লোক পণ্য।
"তালের পাখা
প্রাণের সখা,
দিয়ো দেখা"
প্রাণের সখা,
দিয়ো দেখা"
বর্তমানে প্লাস্টিকের হাত পাখা প্রচলন হলেও তালের হাত পাখা বা খেজুর পাতা, কাপড়ের তৈরি পাখার মর্যাদা নিতে পারেনি। তালের হাত পাখার বাতাস একদম শীতল। বিদ্যুৎ আবিস্কৃত হলেও গ্রামে গঞ্জে এখনো বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি। তার উপর বিদ্যুৎ বিভ্রাট তো আছেই। তাই হাত পাখার প্রসার এখনো কমেনি। রাজা বাদশাদের আমলে আমরা দেখতাম রাজার সিংহাসনের পিছনে দুইজন পাখা হাতে দাঁড়িয়ে থাকত। তাদের কাজ ছিল বিশাল সাইজের এই পাখা ধীরে ধীরে বাতাস করা। হাত পাখা ছাড়াও আরেক ধরনের পাখা ছিল। এই পাখা কাপড়ের তৈরি। মাথার উপর সিলিংয়ে ঝুলানো থাকত মোটা কাপড়। এর চারদিকে মোড়ানো থাকত লালসালু। এর সঙ্গে যুক্ত থাকত দড়ি। দূরে বসে একজন দড়ি ধরে টানত। দড়ির টানে লালসালু যুক্ত মোটা কাপড় এদিক-ওদিক নড়াচড়া করতো। এতে সারা ঘরময় বাতাস খেলে যেত। এক সময় অফিস-আদালতে মাথার উপর সিলিংয়ে ঝুলানো এ ধরনের পাখা টেনে বাতাস করার রেওয়াজ ছিল। বেশি দিন আগের কথা নয়। এই ইংরেজ আমলে এমন কি ইংরেজ আমলের পরেও এ উপমহাদেশে জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে এ ধরনের পাখা টেনে বাতাস করার ব্যবস্থা ছিল। তখন এ কাজের জন্য সরকারি কর্মচারীও নিযুক্ত ছিল। এখন এই ধরনের পাখা না দেখা গেলেও হাত পাখার কদর এখনো কমে নি। কৃষক মাঠে কাজ করছে, আর তার বধু তার জন্য খাবার নিয়ে আসছে এবং সাথে একটি হাত পাখা। কৃষক খাচ্ছে এবং গৃহবধু হাত পাখা দিয়ে বাতাস করছে। এই হাত পাখা নিয়ে অনেক গান কবিতা আছে। একটি জনপ্রিয় গান এই রকম,
''তোমার হাত পাখার বাতাসে
প্রান জুড়িয়ে আসে,
কিছু সময় আরও তুমি
থাকো আমার পাশে''
প্রান জুড়িয়ে আসে,
কিছু সময় আরও তুমি
থাকো আমার পাশে''
এখন বিভিন্ন নকশার পাখা পাওয়া যায়। হাত পাখা দিয়ে চৈনিক নৃত্যও আছে। গ্রামের গৃহবধুরা হাত পাখার মধ্যে অনেক ছড়া এবং শ্লোক লিখে থাকে। এই ধরনের কিছু শ্লোক বা ছড়া নিম্নরূপ,
''বিন্দু বিন্দু সৎকর্ম গড়ে তোলে সুখের প্রাসাদ
বিন্দু বিন্দু লোভে দু:খ, বিন্দু বিন্দু কষ্টে অবসাদ"
"সালাম দিয়াছো যারে, জরি সাজে মখমলের জামায়
গতকাল সে ছিন্ন বেশে ভিক্ষা চাহিয়া ফিরে যায়।"
"গোয়ালার গরু নাই, চাষা কাঁদে রাতে
আমার সন্তান কেমনে থাকে দুধে ভাতে?"
"এক দমের কত বাহাদুরী
মাটির কঙ্কাল সাজে সোনার মোহরে,
গরীবের অর্থ করে চুরি"
বিন্দু বিন্দু লোভে দু:খ, বিন্দু বিন্দু কষ্টে অবসাদ"
"সালাম দিয়াছো যারে, জরি সাজে মখমলের জামায়
গতকাল সে ছিন্ন বেশে ভিক্ষা চাহিয়া ফিরে যায়।"
"গোয়ালার গরু নাই, চাষা কাঁদে রাতে
আমার সন্তান কেমনে থাকে দুধে ভাতে?"
"এক দমের কত বাহাদুরী
মাটির কঙ্কাল সাজে সোনার মোহরে,
গরীবের অর্থ করে চুরি"
হাত পাখা টাঙ্গাইলে বিছুন আবার ময়মনসিংহ তে বিচুইন নামে পরিচিত। অনেকে বাণিজ্যিক ভাবে হাত পাখার ব্যবসা করে লাভবান হচ্ছে।
খড়মঃ
ছবির এই খড়মটি হাছন রাজার। তিনি গৃহের অভ্যন্তরে চলাচলের জন্য খড়ম ব্যবহার করতেন। খড়ম এক প্রকার কাঠের পাদুকা। একখণ্ড কাঠ পায়ের মাপে কেটে খড়ম তৈরি করা হয়। সম্মুখভাগে একটি বর্তুলাকার কাঠের গুটি বসিয়ে দেয়া হয় যা পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও পাশের আঙ্গুলটি দিয়ে আঁকড়ে ধরা হয়। বর্তমানে পা আটকে রাখার জন্য কাঠের গুটির পরিবর্তে রাবার খণ্ড ব্যবহার করা হয়।
এই উপমহাদেশে সুপ্রাচীন কাল থেকে খড়ম ব্যবহার করা হয়। বাংলার প্রস্তর ভাস্কর্যে জুতার ব্যবহার আছে। প্রস্তর সূর্য মূর্তিতে জুতার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। পৌরাণিক অনেক শাস্ত্রে জুতা ব্যবহারের নিয়ম দেখা যায়। জুতা ছিল অস্পর্শ্য। দেবতা ও গুরুজনদের জুতা খুলে প্রনামের নিয়ম ছিল।
সনাতন ধর্মে পাদুকা পুজার প্রচলন আছে। দুর্গাপূজার সময় পাদুকা পুজা করা হয়। রামায়ণে কথিত আছে পিতার আদেশে রামচন্দ্রকে বনবাসে যেতে হয়। তখন তার ভাই ভরত চন্দ্র সিংহাসনের অধিকারী হোন। কিন্তু ভরত চন্দ্র রামচন্দ্রকে সিংহাসনে বসতে অনুরোধ জানান। রামচন্দ্র বনবাস থেকে ফিরে আসতে রাজি হোন নি। ভরত রামচন্দ্রের পাদুকা বা খড়ম মাথায় করে সিংহাসন স্থাপন করে চৌদ্দ বছর রাজ্য শাসন করেন। ধারণা করা হয় এই পাদুকা ছিল খড়ম শ্রেনীর।
এই উপমহাদেশের বিশিষ্ট আউলিয়া হযরত শাহজালাল(রহঃ) খড়ম ব্যবহার করতেন। তাঁর ব্যবহৃত খড়ম তাঁর সমাধিস্থলে সংরক্ষিত আছে। বর্তমানে খড়মে ব্যবহারর নেই। সেই স্থান দখল করে আছে চামড়া ও রাবারের তৈরি পাদুকা। খড়ম পেটার কথা আমরা শুনেছি এখন সেটা জুতা পেটা হয়েছে।
আমাদের লোকছড়ায় খড়ম নিয়ে ছড়া আছে। ছড়াটি এই রকমঃ
ছবির এই খড়মটি হাছন রাজার। তিনি গৃহের অভ্যন্তরে চলাচলের জন্য খড়ম ব্যবহার করতেন। খড়ম এক প্রকার কাঠের পাদুকা। একখণ্ড কাঠ পায়ের মাপে কেটে খড়ম তৈরি করা হয়। সম্মুখভাগে একটি বর্তুলাকার কাঠের গুটি বসিয়ে দেয়া হয় যা পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও পাশের আঙ্গুলটি দিয়ে আঁকড়ে ধরা হয়। বর্তমানে পা আটকে রাখার জন্য কাঠের গুটির পরিবর্তে রাবার খণ্ড ব্যবহার করা হয়।
এই উপমহাদেশে সুপ্রাচীন কাল থেকে খড়ম ব্যবহার করা হয়। বাংলার প্রস্তর ভাস্কর্যে জুতার ব্যবহার আছে। প্রস্তর সূর্য মূর্তিতে জুতার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। পৌরাণিক অনেক শাস্ত্রে জুতা ব্যবহারের নিয়ম দেখা যায়। জুতা ছিল অস্পর্শ্য। দেবতা ও গুরুজনদের জুতা খুলে প্রনামের নিয়ম ছিল।
সনাতন ধর্মে পাদুকা পুজার প্রচলন আছে। দুর্গাপূজার সময় পাদুকা পুজা করা হয়। রামায়ণে কথিত আছে পিতার আদেশে রামচন্দ্রকে বনবাসে যেতে হয়। তখন তার ভাই ভরত চন্দ্র সিংহাসনের অধিকারী হোন। কিন্তু ভরত চন্দ্র রামচন্দ্রকে সিংহাসনে বসতে অনুরোধ জানান। রামচন্দ্র বনবাস থেকে ফিরে আসতে রাজি হোন নি। ভরত রামচন্দ্রের পাদুকা বা খড়ম মাথায় করে সিংহাসন স্থাপন করে চৌদ্দ বছর রাজ্য শাসন করেন। ধারণা করা হয় এই পাদুকা ছিল খড়ম শ্রেনীর।
এই উপমহাদেশের বিশিষ্ট আউলিয়া হযরত শাহজালাল(রহঃ) খড়ম ব্যবহার করতেন। তাঁর ব্যবহৃত খড়ম তাঁর সমাধিস্থলে সংরক্ষিত আছে। বর্তমানে খড়মে ব্যবহারর নেই। সেই স্থান দখল করে আছে চামড়া ও রাবারের তৈরি পাদুকা। খড়ম পেটার কথা আমরা শুনেছি এখন সেটা জুতা পেটা হয়েছে।
আমাদের লোকছড়ায় খড়ম নিয়ে ছড়া আছে। ছড়াটি এই রকমঃ
"হরম বিবি খড়ম পায়
খটটাইয়া হাঁইটা যায়
হাঁটতে গিয়া হরম বিবি
ধুম্মুড় কইরা আছাড় খায়
আছাড় খাইয়া হরম বিবি
ফিরা ফিরা পিছন চায় ...."
খটটাইয়া হাঁইটা যায়
হাঁটতে গিয়া হরম বিবি
ধুম্মুড় কইরা আছাড় খায়
আছাড় খাইয়া হরম বিবি
ফিরা ফিরা পিছন চায় ...."
হুক্কাঃ
এক সময় অতিথি আপ্যায়ন এর অন্যতম উপকরণ ছিল পান-তামাক। তামাক দিয়ে পরিবেশনের সময় এগিয়ে দেয়া হত হুক্কা। একসময় ছিল গ্রাম বাংলার মানুষরা বিড়ি-সিগারেট দেখতো না। তখন তাদের ধুমপানের একমাত্র স্বম্বল ছিল নারিকেল, কাঠ ও মাটির তৈরি কলকি দ্বার নির্মিত হুক্কা। হুক্কা সেবনে প্রয়োজন হতো তামাক ও টিক্কা।
এই অঞ্চলে তামাক নিয়ে আনে পর্তুগীজরা। তারাই এই অঞ্চলে ধূমপানের প্রচলন শুরু করে। আর হুক্কা দিয়ে ধূমপানের প্রচলন শুরু করে মোঘল রা। মনে করা হয় মোঘল এক চিকিৎসক হুক্কার আবিষ্কারক। মোঘল আমলে বাদশা-বেগম থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ হুক্কা টেনেছে।
হুক্কা একটি আরবী শব্দ। আরবে এটা সিসা বা নারগিলা বলে পরিচিত। ইরানে বলে গালয়ুন, উজবেকরা বলে সিলিম। বাংলাদেশে বর্তমানে অনেক সিসা লাউঞ্জ গড়ে উঠেছে। সেখানে আপেল, আম, স্ট্রবেরী সহ বিভিন্ন স্বাদের সিসা পাওয়া যায়।
ছবিতে যে নারিকেলের হুক্কাটা দেখতে পাচ্ছেন, ওটাই আসলে হুক্কা। নিচের অংশটা নারিকেলের , যেটাতে পানি থাকে, ও ধূয়া টানার জন্য একটি ছিদ্র থাকে, মধ্যের অংশটা কাঠের নল, উপরের ক্যাপটা হলো সিলিম বা কল্কি, সিলিমটার মাঝে সীসা বা মাটির এক টুকরা মার্বেল আকৃতির গোলক দেয়া হয় যাতে জ্বলা তামাক পড়ে না যায়।
চিটা গুড়ের সাথে তামাক গুড়া মিশিয়ে মন্ড তৈরি করা হয়, মন্ডটা সিলিমে দেয়া হয়, তামাকের উপরে জ্বলন্ত টিকি (চারকোল) জ্বালিয়ে দেয়া হয়, তারপর নিচের নারিকেলের ছিদ্রে মুখ দিয়ে টান দিলে তামাক জ্বলে ধোঁয়াটা মুখে আসে সেই সীসা বা মাটির এক টুকরা মার্বেল আকৃতির গোলকের পাশ দিয়ে, আভিজাতদের হুক্কা দেখে কেউ কেউ নারিকেলের ছিদ্রে একটা বাঁশ বা নলখাগড়ার ছোট নল লাগান। হুক্কাতে টান দিলে বেশ সুন্দর একটি শব্দ তৈরি হয়।
ছবির এই হুক্কাটি গরীব লোকদের জন্য। অভিজাত লোকেরা এই ধরনের হুক্কা ব্যবহার করেন না। তারা কারুকার্যময় হুক্কা ব্যবহার করেন। সাধারণত সেগুলো পিতলের থাকে।
সিলেট অঞ্চলের একটি ধাঁধা বলি উত্তর দেনঃ
এক সময় অতিথি আপ্যায়ন এর অন্যতম উপকরণ ছিল পান-তামাক। তামাক দিয়ে পরিবেশনের সময় এগিয়ে দেয়া হত হুক্কা। একসময় ছিল গ্রাম বাংলার মানুষরা বিড়ি-সিগারেট দেখতো না। তখন তাদের ধুমপানের একমাত্র স্বম্বল ছিল নারিকেল, কাঠ ও মাটির তৈরি কলকি দ্বার নির্মিত হুক্কা। হুক্কা সেবনে প্রয়োজন হতো তামাক ও টিক্কা।
এই অঞ্চলে তামাক নিয়ে আনে পর্তুগীজরা। তারাই এই অঞ্চলে ধূমপানের প্রচলন শুরু করে। আর হুক্কা দিয়ে ধূমপানের প্রচলন শুরু করে মোঘল রা। মনে করা হয় মোঘল এক চিকিৎসক হুক্কার আবিষ্কারক। মোঘল আমলে বাদশা-বেগম থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ হুক্কা টেনেছে।
হুক্কা একটি আরবী শব্দ। আরবে এটা সিসা বা নারগিলা বলে পরিচিত। ইরানে বলে গালয়ুন, উজবেকরা বলে সিলিম। বাংলাদেশে বর্তমানে অনেক সিসা লাউঞ্জ গড়ে উঠেছে। সেখানে আপেল, আম, স্ট্রবেরী সহ বিভিন্ন স্বাদের সিসা পাওয়া যায়।
ছবিতে যে নারিকেলের হুক্কাটা দেখতে পাচ্ছেন, ওটাই আসলে হুক্কা। নিচের অংশটা নারিকেলের , যেটাতে পানি থাকে, ও ধূয়া টানার জন্য একটি ছিদ্র থাকে, মধ্যের অংশটা কাঠের নল, উপরের ক্যাপটা হলো সিলিম বা কল্কি, সিলিমটার মাঝে সীসা বা মাটির এক টুকরা মার্বেল আকৃতির গোলক দেয়া হয় যাতে জ্বলা তামাক পড়ে না যায়।
চিটা গুড়ের সাথে তামাক গুড়া মিশিয়ে মন্ড তৈরি করা হয়, মন্ডটা সিলিমে দেয়া হয়, তামাকের উপরে জ্বলন্ত টিকি (চারকোল) জ্বালিয়ে দেয়া হয়, তারপর নিচের নারিকেলের ছিদ্রে মুখ দিয়ে টান দিলে তামাক জ্বলে ধোঁয়াটা মুখে আসে সেই সীসা বা মাটির এক টুকরা মার্বেল আকৃতির গোলকের পাশ দিয়ে, আভিজাতদের হুক্কা দেখে কেউ কেউ নারিকেলের ছিদ্রে একটা বাঁশ বা নলখাগড়ার ছোট নল লাগান। হুক্কাতে টান দিলে বেশ সুন্দর একটি শব্দ তৈরি হয়।
ছবির এই হুক্কাটি গরীব লোকদের জন্য। অভিজাত লোকেরা এই ধরনের হুক্কা ব্যবহার করেন না। তারা কারুকার্যময় হুক্কা ব্যবহার করেন। সাধারণত সেগুলো পিতলের থাকে।
সিলেট অঞ্চলের একটি ধাঁধা বলি উত্তর দেনঃ
'তিন জাতের তিন বেটা,
ঘর বানাইলো একটা।
কামার, কুমার ছুতার বেটা,
উপরে কামার, মাঝে ছুতার,
তলার মাঝে গাছের গুটা,
নাম কও চাই পন্ডিত বেটা।'
ঘর বানাইলো একটা।
কামার, কুমার ছুতার বেটা,
উপরে কামার, মাঝে ছুতার,
তলার মাঝে গাছের গুটা,
নাম কও চাই পন্ডিত বেটা।'
(সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণঃ হুক্কা স্বাস্থ্যর জন্য ক্ষতিকারক)
লেখাটি সংগ্রহ করা হয়েছে লোরক সোসাইটি হতে।
সম্পাদনায়ঃ জানা অজানার পথিক।
লোরক সোসাইটির একটি খোলা চিঠিঃ
শুভেচ্ছা নিবেন। অনেকেই বলে থাকেন সংস্কৃতি হচ্ছে একটি দেশের পোশাক। যদি আমরা সেই সংস্কৃতি থেকে দূরে থাকি তাহলে এর প্রভাব কতটা ভয়াবহ হতে পারে তা কখনো কী ভেবে দেখেছেন? লোকসংস্কৃতি আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। বাংলার লোকগান, লোকছড়া, লোকগল্প, লোকখেলা কতই না আকর্ষণীয় এবং চমকপ্রদ। আমাদের শৈশব ছিল ছড়াময়। দাদি-নানির মুখে গল্প শুনে আমরা ঘুমিয়ে পড়তাম। লোকসংস্কৃতির এই উপাদান একসময় রাজা থেকে প্রজা, আমির থেকে গরিব, বুড়ো থেকে শিশু সবার আনন্দ বিনোদনের মাধ্যম ছিল। কিন্তু বিশ্বায়ন এর প্রভাবে ও দিন দিন যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে আজ লোকসংস্কৃতি হুমকির সম্মুখীন। এখনকার সময়ের কোন বালককে যদি গোল্লাছুট খেলার কথা বলা হয় তাহলে সে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকবে। এভাবে চলতে থাকলে আরও কিছু দিন পর আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির কঙ্কাল বিশেষও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমরা হয়ে যাব বস্ত্রহীন জাতির মত।
দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ ও নিজের সংস্কৃতিকে ভালবেসে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল তরুণ তরুণী “লোকসংস্কৃতি রক্ষা করি (লোরক) সোসাইটি” নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছি। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য হল হারিয়ে যেতে বসা লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ ও প্রচার করা এবং লোকসংস্কৃতির হারানো অতীত ফিরিয়ে আনা। আমরা চাই বিশ্বের দরবারে আমাদের সংস্কৃতিকে সমুন্নত রাখতে। আমাদের এই শুভ উদ্যোগে আপনার সহযোগিতা ও সমর্থন প্রয়োজন। আপনার একটু চেষ্টা রক্ষা করতে পারে আমাদের লোক সংস্কৃতিকে। তাই দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে আসুন আমাদের লোরকের পতাকা তলে। আমরা তরুণেরাই পারি আমাদের লোকসংস্কৃতিকে রক্ষা করে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে। ধন্যবাদ।
লেখাটি সংগ্রহ করা হয়েছে লোরক সোসাইটি হতে।
সম্পাদনায়ঃ জানা অজানার পথিক।
লোরক সোসাইটির একটি খোলা চিঠিঃ
শুভেচ্ছা নিবেন। অনেকেই বলে থাকেন সংস্কৃতি হচ্ছে একটি দেশের পোশাক। যদি আমরা সেই সংস্কৃতি থেকে দূরে থাকি তাহলে এর প্রভাব কতটা ভয়াবহ হতে পারে তা কখনো কী ভেবে দেখেছেন? লোকসংস্কৃতি আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। বাংলার লোকগান, লোকছড়া, লোকগল্প, লোকখেলা কতই না আকর্ষণীয় এবং চমকপ্রদ। আমাদের শৈশব ছিল ছড়াময়। দাদি-নানির মুখে গল্প শুনে আমরা ঘুমিয়ে পড়তাম। লোকসংস্কৃতির এই উপাদান একসময় রাজা থেকে প্রজা, আমির থেকে গরিব, বুড়ো থেকে শিশু সবার আনন্দ বিনোদনের মাধ্যম ছিল। কিন্তু বিশ্বায়ন এর প্রভাবে ও দিন দিন যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে আজ লোকসংস্কৃতি হুমকির সম্মুখীন। এখনকার সময়ের কোন বালককে যদি গোল্লাছুট খেলার কথা বলা হয় তাহলে সে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকবে। এভাবে চলতে থাকলে আরও কিছু দিন পর আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির কঙ্কাল বিশেষও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমরা হয়ে যাব বস্ত্রহীন জাতির মত।
দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ ও নিজের সংস্কৃতিকে ভালবেসে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল তরুণ তরুণী “লোকসংস্কৃতি রক্ষা করি (লোরক) সোসাইটি” নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছি। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য হল হারিয়ে যেতে বসা লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ ও প্রচার করা এবং লোকসংস্কৃতির হারানো অতীত ফিরিয়ে আনা। আমরা চাই বিশ্বের দরবারে আমাদের সংস্কৃতিকে সমুন্নত রাখতে। আমাদের এই শুভ উদ্যোগে আপনার সহযোগিতা ও সমর্থন প্রয়োজন। আপনার একটু চেষ্টা রক্ষা করতে পারে আমাদের লোক সংস্কৃতিকে। তাই দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে আসুন আমাদের লোরকের পতাকা তলে। আমরা তরুণেরাই পারি আমাদের লোকসংস্কৃতিকে রক্ষা করে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে। ধন্যবাদ।
মোহাম্মদ আলামিন (সভাপতি)
লোরক সোসাইটি।
লোরক সোসাইটি।








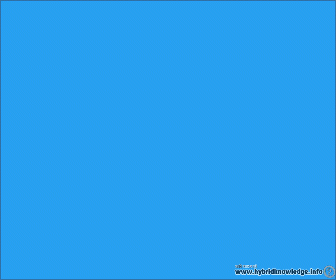



কোন মন্তব্য নেই:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন