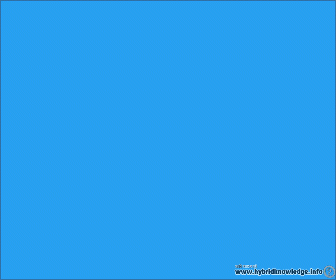আমাদের দেশের মানুষ তো এখন খুব বেড়াতে যায়। আগেকার দিনের মানুষের বেড়ানো কিন্তু এখনকার দিনের মানুষের মতো ছিলো না। আগেকার দিনে মানুষ নানা উপলক্ষে গ্রাম থেকে শহরে যেতো। শহরে গিয়ে নানা কিছু দেখে আনন্দ পেতো। আবার বেশ লম্বা ছুটিতে শহরের মানুষও গ্রামে গিয়ে বেশ ক’দিন খুব মজা করে ঘুরে আসতো। এখন সেই ধারাটিই বদলে গেছে। এখন আর শহরের মানুষ গ্রামে গিয়ে খুব একটা ছুটি কাটায় না। যাদের মোটামুটি সঙ্গতি আছে তারা বাংলাদেশের নানা জায়গায় ছুটি কাটাতে চলে যায়। প্রতিবছরই নানা ছুটিতে কক্সবাজার কিংবা কুয়াকাটা অথবা সিলেটের নানা জায়গায় কত্তো ভীড় হয়! আবার যাদের আরেকটু বেশি সঙ্গতি আছে, তারা আমাদের এশিয়া মহাদেশেরই নানা দেশে যায়; কেউ ভারতে যায়; তবে ভারতে এখন কমই যায়; এখন বেশি যায় সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়ায়। যাদের আরো বেশি সঙ্গতি আছে তারা ইউরোপ, উত্তর আমেরিকার নানান দেশে বেড়াতে যায়। এখনকার দিনের একটা অদ্ভূত দিক কী, আমাদের আশেপাশের দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের যে যোগাযোগ, তারচেয়ে আমাদের দূরের দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ বেশি ভালো। যেমন ধরেন, আমরা যদি নেপালে যেতে চাই, তাতে যে খরচ হবে, তার চেয়ে অনেক কম খরচে মালয়েশিয়া কিংবা ব্যাংকক যাওয়া যায়। সেই সাথে ওসব দেশে যাওয়া আসা করাটাও অনেক সহজ। আবার ধরেন পড়াশুনার জন্যও তো আমরা বিদেশে যাই; মানে জ্ঞানচর্চার জন্য আরকি। সেটাতেও দেখা যায়, ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার দিকেই আমাদের ঝোঁকটা বেশি। সবাই আমেরিকা, কানাডা, ইংল্যান্ড, নরওয়ে এসব দেশে যেতে পারলেই খুশি। যার ফলে কি হচ্ছে জানেন? আমাদের আশেপাশের দেশগুলোর সাথে আমাদের যোগাযোগটা হারিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য চিকিৎসা প্রয়োজনে এখনো আমরা সবার আগে ভারতেই যাই। কিন্তু ওটা তো ব্যতিক্রম।
মোদ্দা কথা হলো, আমাদের ভ্রমণের ব্যাপারটা আমাদের আশেপাশের দেশগুলোর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আমরা এখন আর আমাদের আশেপাশের দেশগুলোতে ঘুরতে যাই না। যেমন আমাদের খুব কাছের একটা দেশ মায়ানমার; কিন্তু ওদের সাথে আবার আমাদের রাজনৈতিক সম্পর্কটা খুব একটা ভালো যাচ্ছে না। যাবে কী করে, ওদের প্রাণের নেত্রী অং-সান সু চি’কে যে ওদের সামরিক শাসকরা একদম গৃহবন্দী করে রেখেছে! এমন পঁচা যে শাসক, তাদের সাথে তো আর আমাদের দেশের নেতা নেত্রীরা গলায় গলায় ভাব রাখতে পারেন না। আর তাই মায়ানমারেও আমাদের দেশের খুব কম লোকই ঘুরতে যায়। আবার আমাদের আশেপাশে ভারতের যে রাজ্যগুলি আছে, যেমন ত্রিপুরা, মেঘালয়, আসাম, এগুলোর মধ্যে এক ত্রিপুরা ছাড়া বাকি জায়গাগুলোতেও কিন্তু খুব একটা যাওয়া হয় না। তুলনায় আমাদের দেশের মানুষ ঢের বেশি যায় ওদেশের কোলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লি, পাঞ্জাবে। তবে আমার বরাবরই মনে হয়, আমরা যদি আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতিকে বুঝতে যাই, আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতির উপকরণ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে যাই, তাহলে আমাদেরকে আমাদের নিজেদের দেশ, আর আমাদের চারপাশের দেশগুলোকে ভালো করে চিনতে হবে; যেই অঞ্চলে আমাদের পূর্বপুরুষরা বাস করতো, সেই অঞ্চলকে চিনতে হবে। আমাদের পূর্বপুরুষরা কোন কোন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিলো জানেন? নিশ্চয়ই বলবেন, কেন, বাংলাদেশ আর পশ্চিমবঙ্গ! ঐ তো ভুল করলে। বইয়ে পড়েন না, বাঙালি মিশ্র জাতি। বিদেশ থেকে কতো কতো জাতির লোকজন এসে আমাদের পূর্বপুরুষদের সাথে মিশে গেছে, তবেই না আমরা বাঙালি হয়েছি। কিন্তু তার আগে যারা এই অঞ্চলে বাস করতো, তারাই না আমাদের প্রকৃত পূর্বপুরুষ, তাই না? সে কিন্তু অনেক আগের কথা, তখনো মহানবী (সঃ) এর জন্মই হয়নি! মানে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, তাঁরা মুসলমান ছিলেন না। আমাদের মধ্যে যারা মুসলমান, তাদের পূর্বপুরুষরা মুসলমান হয়েছেন তুরস্কের লোকেরা, মানে তুর্কিরা বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করার পর। মাথা চুলকোতে লেগে গেলেন নাকি? আরে, ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী’র নাম শোনেননি? যেমন ইয়া লম্বা নাম, তেমন ইয়া লম্বা দেহ, তেমনি ইয়া লম্বা হাত। তিনিই তো প্রথম মুসলমান, যিনি বাংলার ক্ষমতা দখল করেন। আর তারপরেই না এখানকার মানুষ আস্তে আস্তে মুসলমান হতে শুরু করলো। তার আগে এদেশের মানুষ ছিলো সনাতন ধর্মালম্বী (হিন্দু)। আর তারও আগে ছিলেন বৌদ্ধ। পাল রাজাদের নাম শোনেননি? ঐ যে গোপাল, ধর্মপাল? আরে, আস্ক দ্য কিডজ ভাইয়াতে আপনারা সম্রাট অশোকের কলিঙ্গের যুদ্ধের গল্প শুনেছেন না? সেই সম্রাট অশোকও তো ছিলেন পাল বংশের রাজা! এই পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। আর তাদের পরে যে সেন রাজারা রাজত্ব করলেন, তারা ছিলেন হিন্দু।
মোদ্দা কথা হলো, আমাদের ভ্রমণের ব্যাপারটা আমাদের আশেপাশের দেশগুলোর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আমরা এখন আর আমাদের আশেপাশের দেশগুলোতে ঘুরতে যাই না। যেমন আমাদের খুব কাছের একটা দেশ মায়ানমার; কিন্তু ওদের সাথে আবার আমাদের রাজনৈতিক সম্পর্কটা খুব একটা ভালো যাচ্ছে না। যাবে কী করে, ওদের প্রাণের নেত্রী অং-সান সু চি’কে যে ওদের সামরিক শাসকরা একদম গৃহবন্দী করে রেখেছে! এমন পঁচা যে শাসক, তাদের সাথে তো আর আমাদের দেশের নেতা নেত্রীরা গলায় গলায় ভাব রাখতে পারেন না। আর তাই মায়ানমারেও আমাদের দেশের খুব কম লোকই ঘুরতে যায়। আবার আমাদের আশেপাশে ভারতের যে রাজ্যগুলি আছে, যেমন ত্রিপুরা, মেঘালয়, আসাম, এগুলোর মধ্যে এক ত্রিপুরা ছাড়া বাকি জায়গাগুলোতেও কিন্তু খুব একটা যাওয়া হয় না। তুলনায় আমাদের দেশের মানুষ ঢের বেশি যায় ওদেশের কোলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লি, পাঞ্জাবে। তবে আমার বরাবরই মনে হয়, আমরা যদি আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতিকে বুঝতে যাই, আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতির উপকরণ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে যাই, তাহলে আমাদেরকে আমাদের নিজেদের দেশ, আর আমাদের চারপাশের দেশগুলোকে ভালো করে চিনতে হবে; যেই অঞ্চলে আমাদের পূর্বপুরুষরা বাস করতো, সেই অঞ্চলকে চিনতে হবে। আমাদের পূর্বপুরুষরা কোন কোন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিলো জানেন? নিশ্চয়ই বলবেন, কেন, বাংলাদেশ আর পশ্চিমবঙ্গ! ঐ তো ভুল করলে। বইয়ে পড়েন না, বাঙালি মিশ্র জাতি। বিদেশ থেকে কতো কতো জাতির লোকজন এসে আমাদের পূর্বপুরুষদের সাথে মিশে গেছে, তবেই না আমরা বাঙালি হয়েছি। কিন্তু তার আগে যারা এই অঞ্চলে বাস করতো, তারাই না আমাদের প্রকৃত পূর্বপুরুষ, তাই না? সে কিন্তু অনেক আগের কথা, তখনো মহানবী (সঃ) এর জন্মই হয়নি! মানে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, তাঁরা মুসলমান ছিলেন না। আমাদের মধ্যে যারা মুসলমান, তাদের পূর্বপুরুষরা মুসলমান হয়েছেন তুরস্কের লোকেরা, মানে তুর্কিরা বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করার পর। মাথা চুলকোতে লেগে গেলেন নাকি? আরে, ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী’র নাম শোনেননি? যেমন ইয়া লম্বা নাম, তেমন ইয়া লম্বা দেহ, তেমনি ইয়া লম্বা হাত। তিনিই তো প্রথম মুসলমান, যিনি বাংলার ক্ষমতা দখল করেন। আর তারপরেই না এখানকার মানুষ আস্তে আস্তে মুসলমান হতে শুরু করলো। তার আগে এদেশের মানুষ ছিলো সনাতন ধর্মালম্বী (হিন্দু)। আর তারও আগে ছিলেন বৌদ্ধ। পাল রাজাদের নাম শোনেননি? ঐ যে গোপাল, ধর্মপাল? আরে, আস্ক দ্য কিডজ ভাইয়াতে আপনারা সম্রাট অশোকের কলিঙ্গের যুদ্ধের গল্প শুনেছেন না? সেই সম্রাট অশোকও তো ছিলেন পাল বংশের রাজা! এই পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। আর তাদের পরে যে সেন রাজারা রাজত্ব করলেন, তারা ছিলেন হিন্দু।
তো, আমাদের সেই বৌদ্ধ পূর্বপুরুষরা ছড়িয়ে ছিলেন বর্তমান বাংলাদেশ আর পশ্চিমবঙ্গেরও বেশি অঞ্চলে। তারা উত্তরে হিমালয় পর্বতের পাদদেশেও ছিলেন; মানে এখনকার নেপাল, ভূটান, তারপর ভারতের আসাম, মেঘালয়, সিকিম, ত্রিপুরা রাজ্যেও ছিলেন। হলো কি, সেন রাজারা যখন রাজত্ব শুরু করলেন, তখন রাজা যেহেতু হিন্দু, কাজে কাজেই প্রজাদের মধ্যে যারা হিন্দু, তারা একটু বেশি সুবিধা পেতে লাগলেন। আর বৌদ্ধ পণ্ডিত আর সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেদের আর আগের মতো কদর রইলো না। উল্টো সেন রাজারা তাদের উপর কিছুটা রুষ্টই ছিলেন; সেন রাজারা তো আর এদেশের মানুষ ছিলেন না, তাদের হয়তো মনে হতো, এরা তো অন্য ধর্মের লোক, মানে আমাদের শত্রুও হতে পারে। সব মিলিয়ে সেই বৌদ্ধ পণ্ডিত আর সম্ভ্রান্ত লোকেরা এখনকার বাংলায় না থেকে উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশে, নেপালে, ভূটানে, তারপর ভারতের আসামে, মেঘালয়ে, সিকিমে গিয়ে বসতি গাড়লেন। আবার একই ঘটনা ঘটলো মুসলমানরা এদেশের ক্ষমতা দখল করে নিলে। এবার হিন্দু পণ্ডিত আর সম্ভ্রান্ত লোকেরা চলে গেলেন, বসতি গাড়লেন ঐ নেপাল, ভূটান, ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, এরকরম নানা জায়গায়। তার মানে কি দাঁড়ালো? আমাদের আসল সংস্কৃতি যদি আমাদের জানতেই হয়, আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্যকে চিনতেই হয়, আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতির উপকরণকে যদি খুঁজে পেতেই হয়, তাহলে আমাদের আশেপাশের এই অঞ্চলগুলো ঘুরে ঘুরে চেনা ছাড়া, মানে ভ্রমণ করা ছাড়া কোনো গতি নেই! এদের সাথে যে আমাদের সাংস্কৃতিক বন্ধনের একটা সূত্র আছে, একটা আত্মার বন্ধন আছে!
এসব কারণে তো আমার নেপালে যাওয়ার একটা ঝোঁক বরাবরই ছিলো। আরো কয়েকটা কারণ ছিলো। প্রথমত, বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে পুরোনো যে উপকরণ চর্যাপদ ৫১টা কবিতার একটি সংকলন, সেই কবিতাগুলি নেপালে পাওয়া গিয়েছে। এই চর্যাপদ কতোদিনের পুরোনো জানেন? প্রায় ১ হাজার কি তারচেয়েও বেশি দিনের পুরোনো। এ নিয়ে অবশ্য পণ্ডিতরা একমত হতে পারেননি, তবে সবাই মেনে নিয়েছেন যে এটা মোটামুটি ৮০০ থেকে ১২০০ সালের মধ্যে লেখা। আগেকার বই কখনো দেখেছেন? সেগুলো কিন্তু এখনকার বইগুলোর মতো বাঁধানো ছিলো ন। বাঁধাই করবে কি করে, গুটেনবার্গ তো ছাপাখানাই আবিষ্কারই করলেন এই ক’দিন আগে! সেগুলো ছিলো হাতে লেখা পুঁথি। আর সেই পুঁথিগুলোর কিছু মজাও ছিলো। যেমন ধরেন, পুঁথিগুলো তো হাতে লিখতো, তাই এগুলোতে লেখা হতো একটানা, দুই শব্দের মাঝখানে কোনো ফাঁকা থাকতো না। মজার এখানেই শেষ না, পুঁথির লাইন কোন দিক থেকে শুরু হবে তারও কোনো বাঁধাধরা নিয়মও ছিলো না। পুঁথি লেখকের, মানে পুঁথিকারের যদি ভালো লাগে তাহলে সবগুলো লাইন বাম দিক থেকে শুরু করতো, কিংবা এক লাইন বাম দিক থেকে শুরু করে ডান দিকে শেষ করে আবার তার পরের লাইন ডান দিক থেকে বাম দিকে, এভাবেও অনেকে লিখতো! তো এই হাজার বছরের পুরোনো চর্যাপদের পুঁথিটি নেপাল থেকে আবিষ্কার করে আমাদের এখানে নিয়ে আসেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নামের এক পণ্ডিত। সে এক বিশাল গল্প, সে না হয় আরেকদিন বলবো।
এ তো গেলো একটা কারণ। আরেকটা কারণ কি জানো, আমার বরাবরই মনে হতো, চর্যার মতোন আরো অনেক সাহিত্য উপকরণ হয়তো নেপাল এবং তার আশেপাশে পাওয়া যেতে পারে। আর আগে যারা ওখানে এগুলির সন্ধান করেছেন, তারা সেগুলি কিছু কিছু পেয়েছেনও বটে। আমার আবার এসব ব্যাপারে বেশ আগ্রহ। তো সবকিছু মিলিয়ে ঠিক করলাম, নেপালে যাওয়াই সই।
কিন্তু নেপালে যাওয়ার সমস্যাটা হচ্ছে, সেখানে যদি স্থলপথে যেতে হয়, তাহলে কোলকাতা, অথবা দিল্লি আগ্রা যাওয়ার পথ যতোটা ভালো, নেপালের যাওয়ার পথটা অতো ভালো না। এ তো গেলো একটা সমস্যা। আরেকটা বড়ো সমস্যা হচ্ছে, নেপালে যেতে হলে ভারতের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। সুতরাং যাওয়ার সময় একবার আর আসার সময় একবার, মোট দু’বার ভারতীয় ভূখণ্ড অতিক্রম করতে হবে। আর দু’বারই ভিসা পাসপোর্ট ইত্যাদির একটা জটিলতা থাকে। তবে যদি আকাশপথে যাওয়া যায়, মানে প্লেনে যাওয়া যায়, তাহলে এখনো আগে ভিসা না নিয়ে নেপালে গিয়ে পরে ভিসা করিয়ে নিলেও হয়।
তো ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে আমি নেপাল গেলাম। আগেই তো বলেছি, নেপালে যাওয়ার জন্য স্থলপথটা খুব একটা ভালো নয়, যেতে আসতে ভারত পেরুতে হয়, তাতে আবার ভিসা পাসপোর্টের ঝামেলা; সেই তুলনায় আকাশপথ বেশ ভালো। তাতে আবার পরে ভিসা করার একটা সুবিধাও আছে। সুতরাং, আমি প্লেনে করেই নেপাল গেলাম।
এ তো গেলো একটা কারণ। আরেকটা কারণ কি জানো, আমার বরাবরই মনে হতো, চর্যার মতোন আরো অনেক সাহিত্য উপকরণ হয়তো নেপাল এবং তার আশেপাশে পাওয়া যেতে পারে। আর আগে যারা ওখানে এগুলির সন্ধান করেছেন, তারা সেগুলি কিছু কিছু পেয়েছেনও বটে। আমার আবার এসব ব্যাপারে বেশ আগ্রহ। তো সবকিছু মিলিয়ে ঠিক করলাম, নেপালে যাওয়াই সই।
কিন্তু নেপালে যাওয়ার সমস্যাটা হচ্ছে, সেখানে যদি স্থলপথে যেতে হয়, তাহলে কোলকাতা, অথবা দিল্লি আগ্রা যাওয়ার পথ যতোটা ভালো, নেপালের যাওয়ার পথটা অতো ভালো না। এ তো গেলো একটা সমস্যা। আরেকটা বড়ো সমস্যা হচ্ছে, নেপালে যেতে হলে ভারতের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। সুতরাং যাওয়ার সময় একবার আর আসার সময় একবার, মোট দু’বার ভারতীয় ভূখণ্ড অতিক্রম করতে হবে। আর দু’বারই ভিসা পাসপোর্ট ইত্যাদির একটা জটিলতা থাকে। তবে যদি আকাশপথে যাওয়া যায়, মানে প্লেনে যাওয়া যায়, তাহলে এখনো আগে ভিসা না নিয়ে নেপালে গিয়ে পরে ভিসা করিয়ে নিলেও হয়।
তো ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে আমি নেপাল গেলাম। আগেই তো বলেছি, নেপালে যাওয়ার জন্য স্থলপথটা খুব একটা ভালো নয়, যেতে আসতে ভারত পেরুতে হয়, তাতে আবার ভিসা পাসপোর্টের ঝামেলা; সেই তুলনায় আকাশপথ বেশ ভালো। তাতে আবার পরে ভিসা করার একটা সুবিধাও আছে। সুতরাং, আমি প্লেনে করেই নেপাল গেলাম।
আমার নেপাল যাওয়ার যে অনেক দিনের ইচ্ছে ছিলো সে তো আগেই বলেছি। সত্যি বলতে কি, আমার ওখানে যাওয়ার কয়েকটি উদ্দেশ্য ছিলো। একটা হচ্ছে ৮-১০ দিন ওখানে থেকে দেশটাকে দেখা, দেশটাকে চেনা, দেশটাকে জানা। আরেকটা হচ্ছে আমাদের সাহিত্যের সভ্যতার পুরোনো উপকরণগুলো এখনো ওখানে আছে কিনা, বা আর নতুন কোনো উপকরণ খুঁজে পাওয়া যায় কিনা, এগুলো দেখা।
তো ডিসেম্বর মাস আবার নেপালে খুবই ঠাণ্ডার সময়। হিমালয়ের বরফাবৃত অঞ্চল ওখান থেকে খুবই কাছে কিনা। ডিসেম্বরের ঠাণ্ডাতে নেপালের লোকজনই খুব কষ্ট পায়, আর আমার তো একদম জমে যাওয়ার অবস্থা! ইউরোপেও এরকমের ঠাণ্ডা আছে, কিন্তু ইউরোপে ঠাণ্ডা থেকে বাঁচারও অনেক উপায় আছে। ওখানে ঘরে ঘরে উষ্ণতার ব্যবস্থা মানে হিটিং সিস্টেম আছে, রাস্তা ঘাটে চলাফেরার জন্য উপযুক্ত কাপড় চোপড় আছে। নেপালেও এগুলো আছে, কিন্তু অতোটা ভালো না।
নেপালে গিয়ে আমি ওই দেশের রাজধানী কাঠমুণ্ডুর থামেল বলে একটা জায়গায় উঠলাম, সেখানকার একটা হোটেলে। এই থামেলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এই এলাকাটা হচ্ছে পর্যটকদের এলাকা। প্রতি বছর হিমালয় দেখতে সারা পৃথিবী থেকে প্রচুর পর্যটক আসে নেপালে। এই পর্যটকদের বেশির ভাগই আসে শীতের দেশ থেকে, আর ওসব দেশে ডিসেম্বরে ক্রিসমাসের একটা লম্বা ছুটি থাকে, সুতরাং তারা এ সময়টাতেই আসে বেশি। ফলে এই সময়ে থামেলে প্রচুর ভীড় থাকে, অনেকটা আমাদের দেশের ঈদের সময়ের গাউসিয়ার মতো, কিংবা গুলিস্তানের মতো, কিংবা ছুটি হলে সবাই যখন বাড়ি যায় তখনকার সদরঘাটের মতো, প্রচণ্ড ভীড়। আর আমাদের দেশের মতোই সেখানেও কিন্তু ফুটপাথে বিক্রেতারা বসে। ঐ আমাদের হকারদের মতো আরকি! আর এত্তো মানুষ, পুরো রাস্তায় মানুষ গিজগিজ করতে থাকে, পুরো রাস্তা দিয়েই মানুষ হাঁটে। আর এই থামেলের একটা অদ্ভূত বিষয় হল, এখানে আবার গাড়ি খুবই কম। আর যাও বা দু-একটা গাড়ি আসে, সেগুলো মানুষের পিছেপিছেই যায়, খুব বেশি হর্ন দিয়ে মানুষকে বিরক্তও করে না।
যেহেতু মানুষ অনেক বেশি থাকে, কাজেই এ সময় থামেলে থাকার জায়গারও খুব সমস্যা হয়। ছোটো বড়ো হোটেল তো বটেই, যে সব মানুষেরা বাসায় কয়েক দিন থাকার জন্য রুম ভাড়া দেয়, সেগুলোতেও জায়গা পাওয়া যায় না, এত্তো ভীড় হয়। তবে থাকার কষ্ট হলেও খাওয়ার কোনো সমস্যাই হয় না। ওখানে মোটামুটি সব ধরনের খাবারই পাওয়া যায় ভারতীয় বা ইন্ডিয়ান খাবার, তোমাদের প্রিয় ইউরোপিয়ান ফাস্ট ফুড, তারপর নেপালি খাবার, চাইনিজ খাবার, তিব্বতি খাবার, পূর্ব ভারতীয় খাবার, সবই পাওয়া যায়। আবার পকেটের কথা চিন্তা করলে সস্তা খাবার, অল্প দামি খাবার, দামি খাবার, সবই আছে। মোদ্দা কথা যেটা, থামেলে থাকাটা বেশ ব্যয়বহুল, কিন্তু খাওয়া দাওয়া যেমন সস্তা আর তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণও বটে।
তো ডিসেম্বর মাস আবার নেপালে খুবই ঠাণ্ডার সময়। হিমালয়ের বরফাবৃত অঞ্চল ওখান থেকে খুবই কাছে কিনা। ডিসেম্বরের ঠাণ্ডাতে নেপালের লোকজনই খুব কষ্ট পায়, আর আমার তো একদম জমে যাওয়ার অবস্থা! ইউরোপেও এরকমের ঠাণ্ডা আছে, কিন্তু ইউরোপে ঠাণ্ডা থেকে বাঁচারও অনেক উপায় আছে। ওখানে ঘরে ঘরে উষ্ণতার ব্যবস্থা মানে হিটিং সিস্টেম আছে, রাস্তা ঘাটে চলাফেরার জন্য উপযুক্ত কাপড় চোপড় আছে। নেপালেও এগুলো আছে, কিন্তু অতোটা ভালো না।
নেপালে গিয়ে আমি ওই দেশের রাজধানী কাঠমুণ্ডুর থামেল বলে একটা জায়গায় উঠলাম, সেখানকার একটা হোটেলে। এই থামেলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এই এলাকাটা হচ্ছে পর্যটকদের এলাকা। প্রতি বছর হিমালয় দেখতে সারা পৃথিবী থেকে প্রচুর পর্যটক আসে নেপালে। এই পর্যটকদের বেশির ভাগই আসে শীতের দেশ থেকে, আর ওসব দেশে ডিসেম্বরে ক্রিসমাসের একটা লম্বা ছুটি থাকে, সুতরাং তারা এ সময়টাতেই আসে বেশি। ফলে এই সময়ে থামেলে প্রচুর ভীড় থাকে, অনেকটা আমাদের দেশের ঈদের সময়ের গাউসিয়ার মতো, কিংবা গুলিস্তানের মতো, কিংবা ছুটি হলে সবাই যখন বাড়ি যায় তখনকার সদরঘাটের মতো, প্রচণ্ড ভীড়। আর আমাদের দেশের মতোই সেখানেও কিন্তু ফুটপাথে বিক্রেতারা বসে। ঐ আমাদের হকারদের মতো আরকি! আর এত্তো মানুষ, পুরো রাস্তায় মানুষ গিজগিজ করতে থাকে, পুরো রাস্তা দিয়েই মানুষ হাঁটে। আর এই থামেলের একটা অদ্ভূত বিষয় হল, এখানে আবার গাড়ি খুবই কম। আর যাও বা দু-একটা গাড়ি আসে, সেগুলো মানুষের পিছেপিছেই যায়, খুব বেশি হর্ন দিয়ে মানুষকে বিরক্তও করে না।
যেহেতু মানুষ অনেক বেশি থাকে, কাজেই এ সময় থামেলে থাকার জায়গারও খুব সমস্যা হয়। ছোটো বড়ো হোটেল তো বটেই, যে সব মানুষেরা বাসায় কয়েক দিন থাকার জন্য রুম ভাড়া দেয়, সেগুলোতেও জায়গা পাওয়া যায় না, এত্তো ভীড় হয়। তবে থাকার কষ্ট হলেও খাওয়ার কোনো সমস্যাই হয় না। ওখানে মোটামুটি সব ধরনের খাবারই পাওয়া যায় ভারতীয় বা ইন্ডিয়ান খাবার, তোমাদের প্রিয় ইউরোপিয়ান ফাস্ট ফুড, তারপর নেপালি খাবার, চাইনিজ খাবার, তিব্বতি খাবার, পূর্ব ভারতীয় খাবার, সবই পাওয়া যায়। আবার পকেটের কথা চিন্তা করলে সস্তা খাবার, অল্প দামি খাবার, দামি খাবার, সবই আছে। মোদ্দা কথা যেটা, থামেলে থাকাটা বেশ ব্যয়বহুল, কিন্তু খাওয়া দাওয়া যেমন সস্তা আর তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণও বটে।
তখন ওখানে ঘুরে আমার যেটা মনে হয়েছে, ওখানে মৈথিলি সংস্কৃতি আর তিব্বতি সংস্কৃতির একটা মিশ্রণ রয়েছে। নেপাল রাষ্ট্রীয়ভাবে হিন্দু রাষ্ট্র। কিন্তু কী অবাক কাণ্ড! ওখানে যতো না ধুতি পরা হিন্দুদের চোখে পড়লো, তারচেয়ে বেশি দেখলাম মৈথিলি, তিব্বতি লোক। তিব্বতি লামা, বজ্রযানী, এরা আর মৈথিলি বৌদ্ধদের সংখ্যাই মনে হলো ওখানে বেশি!
থামেলের আরেকটা জিনিস আমি খেয়াল করেছি, ওখানে দোকান গুলোর মধ্যে জামা কাপড়ের দোকান, আর আর যতো দোকান বাজারে দেখা যায়, এসবের চেয়ে চিত্রকলা বা ছবির দোকান, তারপর ছোটো ছোটো ভাস্কর্যের দোকান এগুলোই বেশি। ওখানে সবচেয়ে বেশি আছে বোধহয় ছবির দোকান। তারপর ছোটো ছোটো ভাস্কর্যের দোকানও অনেক আছে। আর কতোরকমের যে ভাস্কর্য পাওয়া যায়! লোহার ভাস্কর্যের দোকান, পিতলের ভাস্কর্যের দোকান, পাথরের ভাস্কর্যের দোকান, তারপর বাঁশের ভাস্কর্যের দোকান, এগুলো প্রচুর আছে। মানে, ওখানকার ব্যবসা বাণিজ্যের একটা বড় উপাদানই হল শিল্পকলা। এটা কিন্তু খুবই ভালো। তোমার বাসার পাশে যদি এরকম বেশ কয়েকটা দোকান থাকতো, বেশ মজা হতো না? আর সবচেয়ে বড়ো কথা, এমনি কয়েকটা দোকান থাকলে যেটা হতো, না কিনলেও তুমি অন্তত প্রতিদিন ওগুলো দেখতে পারতে। ফলে তোমার অজান্তেই তোমার ভেতরে ছবি আর ভাস্কর্যের ব্যাপারে বেশ একটা টনটনে ধারণা হয়ে যেতো।
তারপর ওখানে আরো মজার মজার ব্যাপার আছে। হিমালয়ের এক দুর্গম অঞ্চলে গিয়ে দেখি কী, একটা মন্দির! দেবী দূর্গাকে চেনেন না? সেই দেবী দূর্গার মন্দির। তারপর কাঠমুণ্ড শহরের একটা বিখ্যাত মন্দির হচ্ছে রক্তকালী মন্দির। যদি কখনো নেপালে যাওয়া হয়, তবে এই মন্দির কিন্তু দেখতে ভুলবেন না।
আচ্ছা, অনেক তো নেপালের গল্প হলো। আবার চলেন চর্যাপদের কথায় ফিরে আসা যাক। চর্যাপদ বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন হলেও সেটার ভাষা কিন্তু আমাদের এখনকার বাংলা ভাষার মতো না। তখন আমাদের বাংলা ভাষাটা কেবল জন্ম নিচ্ছে কি নিয়েছে। ছোট্ট শিশু যেমন বড়ো না হওয়া পর্যন্ত বোঝা যায় না, ও আসলে কি রকম হবে, খাটো হবে না লম্বা হবে, হাত পা গুলো কেমন হবে, তারপর স্বভাব কেমন হবে, কথা মিষ্টি হবে না পচা হবে, ভাষার ব্যাপারটাও ঠিক তেমনি। ভাষাও মানুষের মতোই অনবরত বদলে যেতে থাকে। শিশুকালে ভাষা অনেকটাই অস্থির থাকে। বয়স যতো বাড়তে থাকে, ভাষা ততোই সুস্থির হতে থাকে, তাকে ততো সহজে চেনা যায়। তবে মানুষের মতো ভাষা একদিন বুড়িয়ে মরে যায় না। যতোদিন সে বদলাতে পারে, মানুষের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে, ততোদিনই ভাষা বেঁচে থাকে। আর তাই তো, রাশভারী সংস্কৃত ভাষা মানুষের মুখের ভাষার সাথে তাল মিলাতে না পেরে কবেই পটল তুলেছে, ওই ভাষায় আর কেউ কথাও বলে না, গল্পও লেখে না। আর আমাদের মিষ্টি বাংলা ভাষা মানুষের জীবন ও আচার ব্যবহারের পরিবর্তনের সাথে সাথে একটু একটু করে বদলে গিয়ে দিব্যি বেঁচে তো আছেই, তাতে কতো কতো ভালো ভালো গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটকও লেখা হচ্ছে।
তো যা বলছিলাম, চর্যাপদের ভাষাটা ঠিক আমাদের পরিচিত বাংলা ভাষা নয়। হঠাৎ শুনলে সেই ভাষাটা কেমন যেনো অচিন অচিন মনে হয়। একটা চর্যা শোনালে ব্যাপারটা ভালো বুঝতে পারবেন। একটা চর্যায় আছে, ‘কাআ তরুবর পঞ্চবি ডালঅ।’
খুব অদ্ভূত লাগছে না চরণটা? কিন্তু একটু খেয়াল করলে বোঝা যাবে, চরণটার মানে হচ্ছে, ‘কায়া বা শরীর হচ্ছে তরু বা গাছের ন্যায়, এর পাঁচটা ডাল আছে’। এই ভাষাকে আমরা বাঙালিরা বলছি বাংলা ভাষায় রচিত। আবার আসামিরা দাবি করছে এটা আসামি ভাষায় রচিত, উড়িয়ারা বলে উড়িয়া ভাষায়, মৈথিলিরা বলে মৈথিলি ভাষায়, ভোজপুরিয়ারা বলে তাদের ভোজপুরিয়া ভাষায়, নেওয়ারিরা বলে তাদের ভাষায় (নেওয়ারি ভাষা) রচিত। এমনকি হিন্দি ভাষাভাষীরাও বলে, এটা তাদের ভাষায় রচিত। আসলে হয়েছে কি, চর্যা যখন লেখা হচ্ছিল, তখন এই সবগুলি ভাষা অনেকটা একই রকম ছিলো। এই সবগুলি ভাষাই একই ভাষা বংশের সদস্য তো, তাই এদের মধ্যে অনেক মিল আছে। হিন্দি ভাষার সাথে যে আমাদের ভাষার অনেক মিল আছে, সে তো আপনারা সবাই খেয়াল করেছো। মজার ব্যাপার কি জানেন? এই সবগুলো ভাষার মধ্যে বাংলার সাথে হিন্দিরই মিল সবচেয়ে কম। তাহলেই বোঝেন, অন্য ভাষাগুলোর সাথে আমাদের মিষ্টি মধুর বাংলা ভাষার কত্তো মিল! আর তখন তো এই সবগুলো ভাষাই শিশুকালে। ফলে যেটা হলো, সবগুলো ভাষার সঙ্গেই চর্যার ভাষার মিল পাওয়া যায়।
এখন প্রশ্ন হলো, চর্যাপদ যদি আমাদেরই হয়, তাহলে আমাদের দেশের এই পুঁথিটা নেপালে গেলো কি করে? ঐ যে আগেই বলেছিলাম, আমাদের দেশে যখন হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠা হলো, পরে আবার তুর্কি বা মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা হলো, তখন অনেকেই দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন, তাদের একটা বড়ো অংশ ছিলো বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক। পালিয়ে তারা নেপাল, ভূটান, সিকিম, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা এরকম নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়লেন। এদেরই কেউ বা কোনো দল হয়তো এই চর্যা বা গানগুলো নিয়ে গিয়েছিলেন নেপালে। তো কোনো ভাবে চর্যাটা ওখানে গেছে এবং সেটা কোনো এক সময়ে নেপালের রাজদরবারে ঠাঁই পেয়েছিলো। পরে নেপালের রাজদরবারের সব পুঁথি ওরা ওদের যে ন্যাশনাল আর্কাইভ, সেখানে নিয়ে গিয়েছিলো। আমি সেই আর্কাইভে গিয়েছিলাম, আমাদের সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শনটিকে একটু দেখতে, ছুঁয়ে দেখতে, পড়ে দেখতে! সুদীর্ঘ দু’দিন চেষ্টা করেও সেই পুঁথিটার কোনো সন্ধান পাওয়া গেলো না! পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, আমার আগেও দু’একজন চেষ্টা করেছিলো, আমার পরেও আমি শুনেছি দু’একজন গিয়েছিলো, তারা কেউ পুঁথিটার সন্ধান পাননি; হতে পারে পুঁথিটা এমন কোথাও আছে যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তেমন হলেই ভালো, অথবা পুঁথিটা নষ্ট হয়ে গেছে।
তবে এই পুঁথির সাধনা যারা করেন, তাদেরকে যে সহজিয়া বলা হতো, সে তো আগেই বলেছি। এখন সেই বৌদ্ধ সহজিয়াদেরই একটি ধারা আছে, বজ্রযানী। আর এই বজ্রযানী ধারার পণ্ডিতদের বলা হয় বজ্রাচার্য। তারা যখন ঐ বজ্রসাধনা করেন, তখন চর্যাপদের গানগুলো বা চর্যাগুলোর মতো এক ধরনের গান সেখানে অনেকটা মন্ত্রের মতো ব্যবহার করেন। আবার যখন তারা বজ্রনৃত্য করেন, নৃত্যের অনুষঙ্গ হিসেবেও এইরকম গান ব্যবহার করেন। অবশ্য তারা জানেনই না যে, প্রাচীন বাংলা বা পূর্ব ভারতীয় ভাষার সাথে তাদের এক রকম সম্পর্ক আছে। এই বজ্রাচার্যরা মোটামুটিভাবে সকলেই নেওয়ার। মনে করা হয়, এরা পূর্ব ভারত থেকে, মানে আমাদের এই দিক থেকে বিভিন্ন সময় নেওয়ার উপত্যকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেছেন। এদের থেকে নেপালিরা আবার খানিকটা ভিন্ন। এখন, বজ্রাচার্যরা তাদের মন্ত্র হিসেবে যেই গান করেন, তারপর নৃত্যের অনুষঙ্গ হিসেবে যেই গান করেন, এই গানগুলোর সাথে বাংলা ভাষার অনেক মিল আছে। এখন প্রশ্ন হলো, এই মিলটা আছে কেনো? আমার অনুমান, আমাদের যে পুরোনো চর্যাগানগুলো, সেগুলিই পরবর্তী সময়ে, ৮০০-১০০০ বছরে ভেঙ্গে ভেঙ্গে এই বজ্রগানগুলো তৈরি হয়েছে।
থামেলের আরেকটা জিনিস আমি খেয়াল করেছি, ওখানে দোকান গুলোর মধ্যে জামা কাপড়ের দোকান, আর আর যতো দোকান বাজারে দেখা যায়, এসবের চেয়ে চিত্রকলা বা ছবির দোকান, তারপর ছোটো ছোটো ভাস্কর্যের দোকান এগুলোই বেশি। ওখানে সবচেয়ে বেশি আছে বোধহয় ছবির দোকান। তারপর ছোটো ছোটো ভাস্কর্যের দোকানও অনেক আছে। আর কতোরকমের যে ভাস্কর্য পাওয়া যায়! লোহার ভাস্কর্যের দোকান, পিতলের ভাস্কর্যের দোকান, পাথরের ভাস্কর্যের দোকান, তারপর বাঁশের ভাস্কর্যের দোকান, এগুলো প্রচুর আছে। মানে, ওখানকার ব্যবসা বাণিজ্যের একটা বড় উপাদানই হল শিল্পকলা। এটা কিন্তু খুবই ভালো। তোমার বাসার পাশে যদি এরকম বেশ কয়েকটা দোকান থাকতো, বেশ মজা হতো না? আর সবচেয়ে বড়ো কথা, এমনি কয়েকটা দোকান থাকলে যেটা হতো, না কিনলেও তুমি অন্তত প্রতিদিন ওগুলো দেখতে পারতে। ফলে তোমার অজান্তেই তোমার ভেতরে ছবি আর ভাস্কর্যের ব্যাপারে বেশ একটা টনটনে ধারণা হয়ে যেতো।
তারপর ওখানে আরো মজার মজার ব্যাপার আছে। হিমালয়ের এক দুর্গম অঞ্চলে গিয়ে দেখি কী, একটা মন্দির! দেবী দূর্গাকে চেনেন না? সেই দেবী দূর্গার মন্দির। তারপর কাঠমুণ্ড শহরের একটা বিখ্যাত মন্দির হচ্ছে রক্তকালী মন্দির। যদি কখনো নেপালে যাওয়া হয়, তবে এই মন্দির কিন্তু দেখতে ভুলবেন না।
আচ্ছা, অনেক তো নেপালের গল্প হলো। আবার চলেন চর্যাপদের কথায় ফিরে আসা যাক। চর্যাপদ বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন হলেও সেটার ভাষা কিন্তু আমাদের এখনকার বাংলা ভাষার মতো না। তখন আমাদের বাংলা ভাষাটা কেবল জন্ম নিচ্ছে কি নিয়েছে। ছোট্ট শিশু যেমন বড়ো না হওয়া পর্যন্ত বোঝা যায় না, ও আসলে কি রকম হবে, খাটো হবে না লম্বা হবে, হাত পা গুলো কেমন হবে, তারপর স্বভাব কেমন হবে, কথা মিষ্টি হবে না পচা হবে, ভাষার ব্যাপারটাও ঠিক তেমনি। ভাষাও মানুষের মতোই অনবরত বদলে যেতে থাকে। শিশুকালে ভাষা অনেকটাই অস্থির থাকে। বয়স যতো বাড়তে থাকে, ভাষা ততোই সুস্থির হতে থাকে, তাকে ততো সহজে চেনা যায়। তবে মানুষের মতো ভাষা একদিন বুড়িয়ে মরে যায় না। যতোদিন সে বদলাতে পারে, মানুষের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে, ততোদিনই ভাষা বেঁচে থাকে। আর তাই তো, রাশভারী সংস্কৃত ভাষা মানুষের মুখের ভাষার সাথে তাল মিলাতে না পেরে কবেই পটল তুলেছে, ওই ভাষায় আর কেউ কথাও বলে না, গল্পও লেখে না। আর আমাদের মিষ্টি বাংলা ভাষা মানুষের জীবন ও আচার ব্যবহারের পরিবর্তনের সাথে সাথে একটু একটু করে বদলে গিয়ে দিব্যি বেঁচে তো আছেই, তাতে কতো কতো ভালো ভালো গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটকও লেখা হচ্ছে।
তো যা বলছিলাম, চর্যাপদের ভাষাটা ঠিক আমাদের পরিচিত বাংলা ভাষা নয়। হঠাৎ শুনলে সেই ভাষাটা কেমন যেনো অচিন অচিন মনে হয়। একটা চর্যা শোনালে ব্যাপারটা ভালো বুঝতে পারবেন। একটা চর্যায় আছে, ‘কাআ তরুবর পঞ্চবি ডালঅ।’
খুব অদ্ভূত লাগছে না চরণটা? কিন্তু একটু খেয়াল করলে বোঝা যাবে, চরণটার মানে হচ্ছে, ‘কায়া বা শরীর হচ্ছে তরু বা গাছের ন্যায়, এর পাঁচটা ডাল আছে’। এই ভাষাকে আমরা বাঙালিরা বলছি বাংলা ভাষায় রচিত। আবার আসামিরা দাবি করছে এটা আসামি ভাষায় রচিত, উড়িয়ারা বলে উড়িয়া ভাষায়, মৈথিলিরা বলে মৈথিলি ভাষায়, ভোজপুরিয়ারা বলে তাদের ভোজপুরিয়া ভাষায়, নেওয়ারিরা বলে তাদের ভাষায় (নেওয়ারি ভাষা) রচিত। এমনকি হিন্দি ভাষাভাষীরাও বলে, এটা তাদের ভাষায় রচিত। আসলে হয়েছে কি, চর্যা যখন লেখা হচ্ছিল, তখন এই সবগুলি ভাষা অনেকটা একই রকম ছিলো। এই সবগুলি ভাষাই একই ভাষা বংশের সদস্য তো, তাই এদের মধ্যে অনেক মিল আছে। হিন্দি ভাষার সাথে যে আমাদের ভাষার অনেক মিল আছে, সে তো আপনারা সবাই খেয়াল করেছো। মজার ব্যাপার কি জানেন? এই সবগুলো ভাষার মধ্যে বাংলার সাথে হিন্দিরই মিল সবচেয়ে কম। তাহলেই বোঝেন, অন্য ভাষাগুলোর সাথে আমাদের মিষ্টি মধুর বাংলা ভাষার কত্তো মিল! আর তখন তো এই সবগুলো ভাষাই শিশুকালে। ফলে যেটা হলো, সবগুলো ভাষার সঙ্গেই চর্যার ভাষার মিল পাওয়া যায়।
এখন প্রশ্ন হলো, চর্যাপদ যদি আমাদেরই হয়, তাহলে আমাদের দেশের এই পুঁথিটা নেপালে গেলো কি করে? ঐ যে আগেই বলেছিলাম, আমাদের দেশে যখন হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠা হলো, পরে আবার তুর্কি বা মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা হলো, তখন অনেকেই দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন, তাদের একটা বড়ো অংশ ছিলো বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক। পালিয়ে তারা নেপাল, ভূটান, সিকিম, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা এরকম নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়লেন। এদেরই কেউ বা কোনো দল হয়তো এই চর্যা বা গানগুলো নিয়ে গিয়েছিলেন নেপালে। তো কোনো ভাবে চর্যাটা ওখানে গেছে এবং সেটা কোনো এক সময়ে নেপালের রাজদরবারে ঠাঁই পেয়েছিলো। পরে নেপালের রাজদরবারের সব পুঁথি ওরা ওদের যে ন্যাশনাল আর্কাইভ, সেখানে নিয়ে গিয়েছিলো। আমি সেই আর্কাইভে গিয়েছিলাম, আমাদের সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শনটিকে একটু দেখতে, ছুঁয়ে দেখতে, পড়ে দেখতে! সুদীর্ঘ দু’দিন চেষ্টা করেও সেই পুঁথিটার কোনো সন্ধান পাওয়া গেলো না! পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, আমার আগেও দু’একজন চেষ্টা করেছিলো, আমার পরেও আমি শুনেছি দু’একজন গিয়েছিলো, তারা কেউ পুঁথিটার সন্ধান পাননি; হতে পারে পুঁথিটা এমন কোথাও আছে যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তেমন হলেই ভালো, অথবা পুঁথিটা নষ্ট হয়ে গেছে।
তবে এই পুঁথির সাধনা যারা করেন, তাদেরকে যে সহজিয়া বলা হতো, সে তো আগেই বলেছি। এখন সেই বৌদ্ধ সহজিয়াদেরই একটি ধারা আছে, বজ্রযানী। আর এই বজ্রযানী ধারার পণ্ডিতদের বলা হয় বজ্রাচার্য। তারা যখন ঐ বজ্রসাধনা করেন, তখন চর্যাপদের গানগুলো বা চর্যাগুলোর মতো এক ধরনের গান সেখানে অনেকটা মন্ত্রের মতো ব্যবহার করেন। আবার যখন তারা বজ্রনৃত্য করেন, নৃত্যের অনুষঙ্গ হিসেবেও এইরকম গান ব্যবহার করেন। অবশ্য তারা জানেনই না যে, প্রাচীন বাংলা বা পূর্ব ভারতীয় ভাষার সাথে তাদের এক রকম সম্পর্ক আছে। এই বজ্রাচার্যরা মোটামুটিভাবে সকলেই নেওয়ার। মনে করা হয়, এরা পূর্ব ভারত থেকে, মানে আমাদের এই দিক থেকে বিভিন্ন সময় নেওয়ার উপত্যকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেছেন। এদের থেকে নেপালিরা আবার খানিকটা ভিন্ন। এখন, বজ্রাচার্যরা তাদের মন্ত্র হিসেবে যেই গান করেন, তারপর নৃত্যের অনুষঙ্গ হিসেবে যেই গান করেন, এই গানগুলোর সাথে বাংলা ভাষার অনেক মিল আছে। এখন প্রশ্ন হলো, এই মিলটা আছে কেনো? আমার অনুমান, আমাদের যে পুরোনো চর্যাগানগুলো, সেগুলিই পরবর্তী সময়ে, ৮০০-১০০০ বছরে ভেঙ্গে ভেঙ্গে এই বজ্রগানগুলো তৈরি হয়েছে।
কিন্তু সমস্যা হলো ব্যাপারটা নিশ্চিত করতে হলে আমাদেরকে আরো বেশি বেশি করে নেপালে গিয়ে অনুসন্ধান করতে হবে। তাহলে হয়তো একদিন ঠিকই কেউ প্রমাণ করে দেবে, এই বজ্রগানগুলোও আমাদের বাংলা ভাষারই সম্পদ। কেবল দূরে দূরে থাকার কারণে বদলানোর সময় ঠিক আমাদের বাংলার মতো না হয়ে অন্য রকম হয়ে গেছে। অনেকটা প্রবাসে বড়ো হওয়া সন্তানের মতোন।
আর তারচেয়েও বড়ো কথা, নেপাল তো আমাদেরই প্রতিবেশি। আর সে দেশের সভ্যতা সংস্কৃতিও কিন্তু আমাদেরই মত। হবে না, এক সময় যে আমাদের এখান থেকেও অনেকে গিয়ে ঐ দেশে বাসস্থাপন করেছে! সুতরাং, ওদেরকে না চিনলে, ওই দেশ না দেখলে আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতিকেও তো আমরা চিনতে পারবো না। ওরা কিন্তু আমাদের অনেক ঐতিহ্যই সংরক্ষণ করে। যেমন ধরেন, আমি ওখানকার এক পুরোনো পাণ্ডুলিপির দোকানে গিয়ে দেখি চণ্ডীমঙ্গলের অনেকগুলি পুঁথি তাদের কাছে আছে। আবার ‘স্বয়ম্ভূ’ বলে ওই দেশে একটা জায়গা আছে। সেই জায়গার বিশেষত্ব কি জানেন? সেখানে বসে মুনিদত্ত নামে এক পণ্ডিত চর্যাপদের কবিতাগুলোর টীকা লিখেছিলেন। আসলে চর্যাপদের কবিতাগুলো তো বৌদ্ধ সহজিয়াদেরই সাধন মন্ত্র ছিলো। পণ্ডিতরা এগুলো লিখতেন তাদের শিষ্যদের উদ্দেশ্যে। আর তাই এগুলো ছিলো অনেকটা ধাঁধার মতো; সাধারণভাবে পড়লে একটা অর্থ পাওয়া যেতো। কিন্তু আসল অর্থ অন্য রকম, ধাঁধার মতো লুকোনো থাকতো। মুনিদত্ত এই কবিতাগুলোর সেই লুকোনো অর্থগুলোই টীকা আকারে লিখে দিয়েছিলেন। আর যেখানে এগুলো লিখেছিলেন, সেই স্বয়ম্ভূতে এখন বজ্রাচার্যরা বাস করেন। আর আগেই তো বললাম, ধারণা করা হয়, তাদের অনেকেই আসলে আমাদের এই অঞ্চল থেকে, মানে পূর্ব ভারত থেকে ওখানে গিয়েছিলেন। আর ওখানে থাকতে থাকতে এখন পুরোদস্তুর নেওয়ারি হয়ে গেছেন। তাহলে ওখানে যে চর্যাপদের মতো আমাদের সাহিত্য সভ্যতার আরো কোনো উপকরণ নেই, তা কে বলতে পারে! আর বললামই তো, আমার মনে হয়েছে, ওদের এই বজ্রগানগুলোও সেই চর্যাপদের সময়েরই অন্য অন্য চর্যা গানের ভাঙা রূপ।
এই জন্যই বলছিলাম, অনেক দূরের দূরের দেশে ঘুরতে না গিয়ে আমাদের আশেপাশের অঞ্চলে ঘুরতে যাই, তাতে কিন্তু আখেরে আমাদেরই লাভ; আমরা আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি সম্পর্কে যেমন জানতে পারবো, তেমনি আমাদের সাহিত্যের নতুন নতুন কত কিছু জানতে পারবো! আর আমাদের আশেপাশের এই দেশগুলোও কিন্তু কম সুন্দর না। আমাদের দেশেও যেমন অনেক জায়গা আছে, অনেক সুন্দর, কিন্তু আমরা জানি না বলে যেতে পারি না; আমাদের আশেপাশের দেশগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু সেই সমস্যা নেই। হিমালয় পর্বতমালার কথা কি আপনারা জানেন না? সেখানকার পাহাড়গুলো কিন্তু সুইজারল্যান্ডের পাহাড় থেকে মোটেও কম সুন্দর নয়। তারপর আমাদের আরেক প্রতিবেশি দেশ ভূটান সেটাও কিন্তু অনেক সুন্দর; সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক, মালয়েশিয়ার চেয়ে এই দেশটিও কম সুন্দর না। কেবল যাওয়া আসার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা আছে। কিন্তু সমস্যাই যদি না থাকে, তবে আর ভ্রমণের রোমাঞ্চ থাকলো কোথায়? অ্যাডভেঞ্চার, রহস্য আর নতুনকে জানা এই তিনের সম্মিলন হলেই না সেটা একটা আদর্শ ভ্রমণ হবে, তাই না?
লেখকঃ সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ।
সম্পাদকঃ জানা অজানার পথিক।
আর তারচেয়েও বড়ো কথা, নেপাল তো আমাদেরই প্রতিবেশি। আর সে দেশের সভ্যতা সংস্কৃতিও কিন্তু আমাদেরই মত। হবে না, এক সময় যে আমাদের এখান থেকেও অনেকে গিয়ে ঐ দেশে বাসস্থাপন করেছে! সুতরাং, ওদেরকে না চিনলে, ওই দেশ না দেখলে আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতিকেও তো আমরা চিনতে পারবো না। ওরা কিন্তু আমাদের অনেক ঐতিহ্যই সংরক্ষণ করে। যেমন ধরেন, আমি ওখানকার এক পুরোনো পাণ্ডুলিপির দোকানে গিয়ে দেখি চণ্ডীমঙ্গলের অনেকগুলি পুঁথি তাদের কাছে আছে। আবার ‘স্বয়ম্ভূ’ বলে ওই দেশে একটা জায়গা আছে। সেই জায়গার বিশেষত্ব কি জানেন? সেখানে বসে মুনিদত্ত নামে এক পণ্ডিত চর্যাপদের কবিতাগুলোর টীকা লিখেছিলেন। আসলে চর্যাপদের কবিতাগুলো তো বৌদ্ধ সহজিয়াদেরই সাধন মন্ত্র ছিলো। পণ্ডিতরা এগুলো লিখতেন তাদের শিষ্যদের উদ্দেশ্যে। আর তাই এগুলো ছিলো অনেকটা ধাঁধার মতো; সাধারণভাবে পড়লে একটা অর্থ পাওয়া যেতো। কিন্তু আসল অর্থ অন্য রকম, ধাঁধার মতো লুকোনো থাকতো। মুনিদত্ত এই কবিতাগুলোর সেই লুকোনো অর্থগুলোই টীকা আকারে লিখে দিয়েছিলেন। আর যেখানে এগুলো লিখেছিলেন, সেই স্বয়ম্ভূতে এখন বজ্রাচার্যরা বাস করেন। আর আগেই তো বললাম, ধারণা করা হয়, তাদের অনেকেই আসলে আমাদের এই অঞ্চল থেকে, মানে পূর্ব ভারত থেকে ওখানে গিয়েছিলেন। আর ওখানে থাকতে থাকতে এখন পুরোদস্তুর নেওয়ারি হয়ে গেছেন। তাহলে ওখানে যে চর্যাপদের মতো আমাদের সাহিত্য সভ্যতার আরো কোনো উপকরণ নেই, তা কে বলতে পারে! আর বললামই তো, আমার মনে হয়েছে, ওদের এই বজ্রগানগুলোও সেই চর্যাপদের সময়েরই অন্য অন্য চর্যা গানের ভাঙা রূপ।
এই জন্যই বলছিলাম, অনেক দূরের দূরের দেশে ঘুরতে না গিয়ে আমাদের আশেপাশের অঞ্চলে ঘুরতে যাই, তাতে কিন্তু আখেরে আমাদেরই লাভ; আমরা আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি সম্পর্কে যেমন জানতে পারবো, তেমনি আমাদের সাহিত্যের নতুন নতুন কত কিছু জানতে পারবো! আর আমাদের আশেপাশের এই দেশগুলোও কিন্তু কম সুন্দর না। আমাদের দেশেও যেমন অনেক জায়গা আছে, অনেক সুন্দর, কিন্তু আমরা জানি না বলে যেতে পারি না; আমাদের আশেপাশের দেশগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু সেই সমস্যা নেই। হিমালয় পর্বতমালার কথা কি আপনারা জানেন না? সেখানকার পাহাড়গুলো কিন্তু সুইজারল্যান্ডের পাহাড় থেকে মোটেও কম সুন্দর নয়। তারপর আমাদের আরেক প্রতিবেশি দেশ ভূটান সেটাও কিন্তু অনেক সুন্দর; সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক, মালয়েশিয়ার চেয়ে এই দেশটিও কম সুন্দর না। কেবল যাওয়া আসার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা আছে। কিন্তু সমস্যাই যদি না থাকে, তবে আর ভ্রমণের রোমাঞ্চ থাকলো কোথায়? অ্যাডভেঞ্চার, রহস্য আর নতুনকে জানা এই তিনের সম্মিলন হলেই না সেটা একটা আদর্শ ভ্রমণ হবে, তাই না?
লেখকঃ সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ।
সম্পাদকঃ জানা অজানার পথিক।